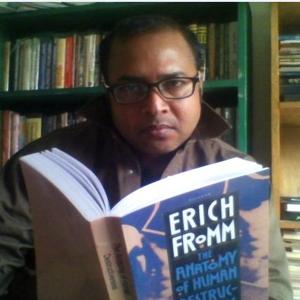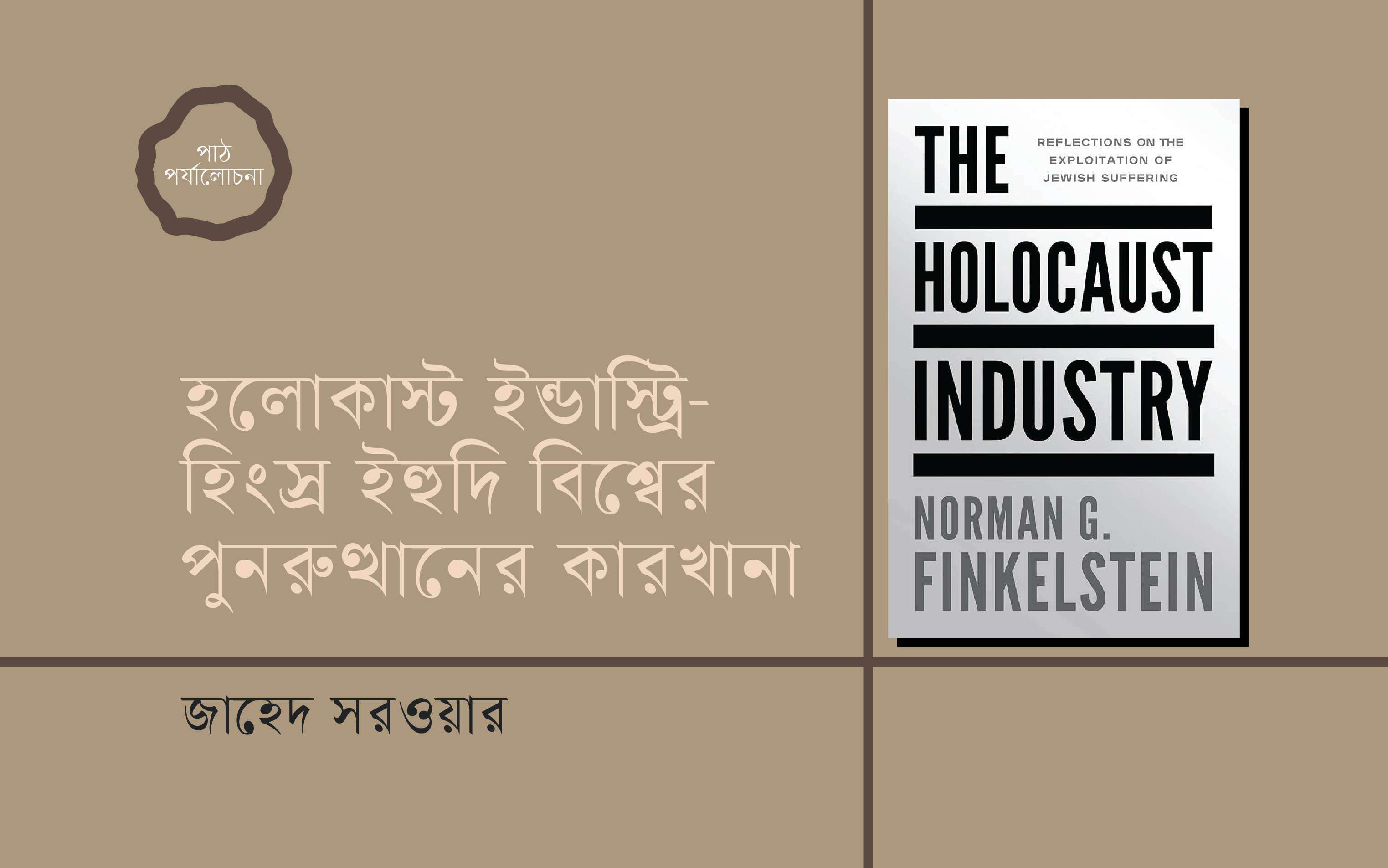
[যদি কোনো সত্যকে নিয়মিতভাবে প্রশ্ন না করা হয়, তাহলে সেটি শেষমেশ অতিরঞ্জনে মিথ্যায় পরিণত হয়- জন স্টুয়ার্ট মিল]
আমরা যখন ছোট ছিলাম মানে পড়তে শিখছি সবেমাত্র। তখন পড়তাম আনা ফ্রাঙ্গের ডায়েরি। পড়তাম ভীতিকর সব হলোকাস্টের কাহিনি। হৃদয় ব্যাতীত হতো। চোখ দিয়ে বেরুতো পানি। লাখ লাখ মানুষকে গ্যাসচেম্বারে মারা হলো। মানুষ মারার কত রকম পদ্ধতি আছে সবই ব্যবহার করা হয়েছে হলোকাস্টে। কত সাহিত্য কত কবিতা কত চলচ্চিত্র কত বক্তৃতা এই হলোকাস্ট নিয়ে। হিটলারের নামও যেন উচ্চারণ করা যেতো না। কেউ যদি হলোকাস্টের বিরুদ্ধে বলে বা জার্মানিদের প্রতি মায়া দেখায় মুহুর্তেই সে হয়ে যায় বিশ্বের জন্য যেন অর্বাচীন। এখন প্রশ্ন উঠছে সচেতন বিশ্ব মহলে এই সব আবেগের জর্জরিত কাহিনি কি আসলেই সত্য? এই হলোকাস্টকে কাজে লাগিয়ে ইহুদিরা স্বয়ং হয়ে উঠেছে হিটলারের চাইতেও ভয়াবহ। হলোকাস্টকে ঘিরে ইউরোপের দেশগুলো থেকে ইহুদিদের চাঁদাবাজির অর্থই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অন্য একটা জাতি নিধনে। এসব যদিও বলতে মানা তবুও খোদ ইহুদি লেখক নরম্যান জি. ফিঙ্কেলস্টেইন এসব নিয়ে লিখেছেন এক দুর্দান্ত বই হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি। এটি একটি বিতর্কিত অভিশংসনমূলক গ্রন্থ- যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে কিছু মানুষ হলোকাস্টের ট্র্যাজেডিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে।
এই বৈপ্লবিক ও বিতর্কিত গবেষণামূলক বইয়ে ফিঙ্কেলস্টেইন আমেরিকান সংস্কৃতিতে হলোকাস্টের অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুরু করে সাম্প্রতিক ক্ষতিপূরণ চুক্তিগুলোর একটি উদ্বেগজনক পর্যালোচনা করেন। তিনি যুক্তি দেন, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের সামরিক শক্তি যখন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তা মিলে যায়, তখনই আমেরিকায় হলোকাস্টের স্মৃতি এক ব্যতিক্রমী গুরুত্ব পেতে শুরু করে। আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতারা ইসরায়েলের এই কৌশলগত উত্থানে আনন্দিত হয় এবং, ফিঙ্কেলস্টেইনের মতে, হলোকাস্টকে তারা ব্যবহার করে নিজেদের নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব জাহির করতে।
এই নেতৃস্থানীয়দের হলোকাস্ট ব্যাখ্যা প্রায়ই প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, এবং এগুলো ব্যবহৃত হয় ইসরায়েল ও এর সমর্থকদের প্রতি যে কোনো সমালোচনাকে দমন করতে। তিনি হলোকাস্ট জালিয়াতদের মধ্যে যেমন জারজি কোসিনস্কি ও বেঞ্জামিন উইলকোমিরস্কি-র কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তেমনি লেখক ড্যানিয়েল গোল্ডহাগেন-এর মতো চরমপন্থীদের কথাও তুলে ধরেন, যাঁরা হলোকাস্ট স্মৃতির একধরনের উগ্র, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।
ফিঙ্কেলস্টেইনের মতে, নাৎসি গণহত্যার শিকারদের স্মৃতিকে সবচেয়ে বড় হুমকি দেয় তথাকথিত হলোকাস্টের "রক্ষাকরা" নিজেরাই- হলোকাস্ট অস্বীকারকারীরা নয়।
বহু অপ্রকাশিত উৎসের ওপর ভিত্তি করে তিনি ইউরোপীয় দেশগুলো এবং প্রকৃত ইহুদি দাবিদারদের উপর চালানো "ডাবল শেকডাউনের" (দ্বৈত ব্ল্যাকমেইল) রহস্য উন্মোচন করেন এবং উপসংহারে বলেন- "হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি এখন একেবারে প্রকাশ্য চাঁদাবাজিতে রূপ নিয়েছে।”
গভীরভাবে গবেষণালব্ধ ও শক্তিশালী যুক্তিনির্ভর এই বইটি আরও উদ্বেগজনক এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠে কারণ এটি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলে, যা সচরাচর আলোচনার বাইরে থাকে।
এই বেস্টসেলারের একটি বিধ্বংসী নতুন পরিশিষ্টে, ফিঙ্কেলস্টেইন দেখিয়েছেন কীভাবে সুইস ব্যাংকগুলোর ব্ল্যাকমেইলের ঘটনাকে হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি চেপে গেছে। এছাড়াও একটি নতুন সংযুক্তিতে তিনি হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রিকে রক্ষাকবচ দিতে চাওয়া একটি প্রভাবশালী লেখার ভিত্তিকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলেন। ফিঙ্কেলস্টেইন দেখান, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশকে ইহুদি সংগঠনগুলোর মাধ্যমে চাপ দিয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থের বড় অংশ প্রকৃত ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছেনি। বরং এটি গিয়েছে কিছু নির্দিষ্ট সংগঠন ও নেতাদের পকেটে। একে তিনি বলেন “ডাবল শেকডাউন"- ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং প্রকৃত হলোকাস্ট সারভাইভার উভয়ের প্রতিই শোষণ।
নরম্যান জি. ফিঙ্কেলস্টেইন-এর The Holocaust Industry একটি সাহসী, তীক্ষ্ণ ও বিতর্ক সৃষ্টিকারী গ্রন্থ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের উপর চালানো গণহত্যার (হলোকাস্ট) স্মৃতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
এই বইয়ে ফিঙ্কেলস্টেইন যুক্তি দেন, হলোকাস্টকে একটি নৈতিক শিক্ষার স্মৃতি হিসেবে ধারণ করার পরিবর্তে একে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
লেখক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী কিছু ইহুদি নেতারা ইসরায়েলের কৌশলগত গুরুত্বকে কাজে লাগিয়ে, হলোকাস্টের ট্র্যাজেডিকে ব্যবহার করেন নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য। এই স্মৃতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তারা ইসরায়েলের নীতির সমালোচনাকে দমন করেন।
লেখক বলেন, যারা নিজেদের “হলোকাস্ট মেমোরি-রক্ষক" বলে দাবি করেন, তারা প্রায়ই ইতিহাসকে নিজেদের মতো করে সাজান। হলোকাস্ট অস্বীকারকারীদের চেয়ে এই বিকৃতি বেশি বিপজ্জনক, কারণ তা মূল সত্যকেই বিকল করে দেয়।
ফিঙ্কেলস্টেইনের মূল লক্ষ্য হলো হলোকাস্টকে রাজনীতি ও লোভের হাত থেকে মুক্ত করা। তিনি চান এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের স্মৃতি যেন সততার সঙ্গে রক্ষিত হয়- কতিপয়ের নোংরা হাতে ব্যবহৃত না হয়। তিনি স্পষ্ট করে বলতে চান: হলোকাস্ট ইসরায়েলি আগ্রাসনের যৌক্তিকতা নয়। হলোকাস্ট সাংবাদিক, একাডেমিক বা সাধারণ মানুষের সমালোচনার অধিকার হরণ করতে পারে না। হলোকাস্ট ভুক্তভোগীদের ব্যক্তিগত ব্যথা, একে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হলে সেটি অনৈতিকতায় পর্যবসিত হয়।
এই বই প্রকাশের পর লেখক তীব্র সমালোচনার শিকার হন। অনেক ইহুদি সংগঠন ও ব্যক্তিরা তাকে "আত্মবিরোধী ইহুদি" ও "অপরাধপ্রবণ ইতিহাসবিদ" আখ্যা দেন। অন্যদিকে, অনেক একাডেমিক ও মানবাধিকার কর্মীরা তাকে সাহসী ও নৈতিকভাবে সৎ চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
The Holocaust Industry একটি ব্যতিক্রমধর্মী বই, যা শুধু ইতিহাস নয়, স্মৃতি, নৈতিকতা, রাজনীতি ও অর্থনীতির ঘন সীমানায় অবস্থান করে। ফিঙ্কেলস্টেইন ইতিহাসকে ব্যবহার করে সত্য বলার ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি যে প্রশ্নগুলো তোলেন, তা সহজ নয়- কিন্তু আমাদের সাহসিকতার সঙ্গে ভাবতে শেখায়।
তিনি আমাদের দেখান যে একটা হলোকাস্টের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ও পুঁজি করে বিশ্বের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ইহুদিরা। ইউরোপিয় বহুদেশকে কলোকাস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচুর চাঁদাবাজি করেছে। নিয়েছে কাড়ি কাড়ি অর্থ। সেই অর্থ তারা ব্যায় করছে আরব দেশগুলোকে আক্রমণের অস্ত্রের যোগান হিসাবে। আজকে ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা একদিক থেকে হলোকাস্টেরই দান। অথচ ইহুদিদের হত্যা করেছে ইউরোপিয়রা কিন্তু ইহুদিরা হত্যা করছে আরবদের। ইতিমধ্যে তারা বিশ্বে হিটলারকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।
এই “হলোকাস্ট” কেবল এলোমেলো এক গঠিত রূপ নয়, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নির্মাণ, যার মূল মতবাদগুলো রাজনৈতিক ও শ্রেণিগত স্বার্থ বহন করে। বাস্তবিক অর্থে, এই “হলোকাস্ট” একটি অত্যন্ত কার্যকর মতাদর্শিক অস্ত্র হয়ে উঠেছে।
এই অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী একটি সামরিক রাষ্ট্র, যাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস ভয়াবহ, তারা নিজেদের উপস্থাপন করেছে একটি “ভুক্তভোগী রাষ্ট্র” হিসেবে। একইভাবে, আমেরিকার সবচেয়ে সফল একটি জাতিগোষ্ঠীও এই ভুক্তভোগী পরিচয় ধারণ করে নিয়েছে।
এই ভুয়া ভুক্তভোগী পরিচয় থেকে বিশাল সুবিধা পাওয়া যায়- সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে কোনো সমালোচনার বিরুদ্ধে অজেয় এক প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠা, সে সমালোচনা যতই ন্যায্য হোক না কেন। যারা এই সুবিধা ভোগ করছে, তারা সেই নৈতিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত নয়, যা সাধারণত এমন ক্ষমতার অনুষঙ্গ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এলি উইজেল-এর “হলোকাস্টের সরকারি ব্যাখ্যাদাতা” হিসেবে আবির্ভাব কোন কাকতালীয় বিষয় নয়। স্পষ্টত, তিনি এই অবস্থানে আসেননি তার মানবিকতা বা সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য। বরং তিনি এই ভূমিকা পালন করছেন কারণ তিনি নিখুঁতভাবে সেই সব মতবাদ উচ্চারণ করেন যা “হলোকাস্ট” মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখে এবং যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলো রক্ষা পায়।
নিজের নাৎসি গণহত্যার প্রতি আগ্রহ বিষয়ে লেখক বলেন, আমার বাবা-মা দুজনেই ছিলেন ওয়ারস র গেটো এবং নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বেঁচে যাওয়া মানুষ। বাবা-মায়ের বাইরে, উভয় পরিবারের সব সদস্যই নাৎসিদের হাতে নিহত হন। আমার মনে পড়ে, আমার হলোকাস্ট নিয়ে প্রথম স্মৃতি হলো- স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, আমার মা টিভির সামনে স্থির হয়ে বসে আছেন- দেখছেন আডলফ আইখম্যানের বিচার (১৯৬১)। যদিও তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন ক্যাম্প থেকে মাত্র ষোল বছর আগে, তবুও আমার কাছে আমার বাবা-মায়ের সেই অতীতের সঙ্গে একটা গভীর দূরত্ব ছিল, যেটা কখনও পেরোনো সম্ভব হয়নি। আমার মায়ের পরিবারের কিছু ছবি আমাদের ড্রয়িংরুমের দেয়ালে টাঙানো ছিল। (বাবার পরিবারের কারও ছবি যুদ্ধের পর বেঁচে ছিল না।)
আমি কখনোই বুঝে উঠতে পারিনি, আমার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক। তারা ছিলেন আমার মায়ের বোনেরা, ভাই ও বাবা-মা, কিন্তু আমার নিজের দৃষ্টিতে তারা কখনো আমার খালা-খালু বা দাদা-দাদি হয়ে উঠতে পারেননি। শিশু অবস্থায় আমি পড়েছিলাম John Hersey-এর The Wall আর Leon Uris-এর Mila 18- দুটোই ওয়ারশ গেটোর কল্পভিত্তিক বিবরণ। (আজও মনে আছে, আমার মা একবার বলেছিলেন- The Wall পড়তে পড়তে এতটাই ডুবে গিয়েছিলেন যে সাবওয়েতে তার স্টেশন মিস হয়ে যায়।) আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনোই কল্পনায় সেই সময়ের সঙ্গে আমার বাবা-মাকে যুক্ত করতে পারিনি। সত্যি বলতে, এখনও পারি না।
এই অংশটি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বেদনার সাথে সাথে একটি তীক্ষ্ণ একাডেমিক সমালোচনার সংমিশ্রণ- যেখানে তিনি "স্মৃতি" শব্দটির পেছনে থাকা রাজনীতি ও মতাদর্শের মুখোশ উন্মোচন করেন।
তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই- এই রহস্যময় উপস্থিতির বাইরে, লেখকের শৈশবে নাৎসি গণহত্যা (হলোকাস্ট) কোনো সময় প্রবেশ করেনি। এর প্রধান কারণ ছিল, তার পরিবারের বাইরের কেউ কখনোই গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি বা আগ্রহ দেখায়নি এই বিষয়ে। লেখকের শৈশবের বন্ধুবৃত্ত ছিল বইপড়া ও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে উৎসাহী বিতর্কে আগ্রহী। কিন্তু তিনি বলছেন- একজন বন্ধুও (বা কোনো বন্ধুর অভিভাবকও) একবারও জিজ্ঞেস করেনি আমার মা-বাবা কী সহ্য করেছিলেন। এটা কোনো শ্রদ্ধাসূচক নীরবতা ছিল না- এটা ছিল নিছক উদাসীনতা। এই প্রেক্ষাপটে যখন পরবর্তী দশকগুলোতে হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এত আবেগের বিস্ফোরণ দেখা যায়, তখন তার প্রতি সংশয়ী না হয়ে উপায় থাকে না। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমেরিকান ইহুদিদের দ্বারা "নাৎসি হলোকাস্টের পুনরাবিষ্কার" সম্ভবত সেই ইতিহাস ভুলে যাওয়ার চেয়েও খারাপ ছিল। সত্যি, আমার বাবা-মা সেই যন্ত্রণার স্মৃতি নিজের মধ্যে গোপনে বহন করতেন; তাদের ভোগান্তি কখনো জনসমক্ষে স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু, সেটা কি ভালো ছিল না, এখনকার মতো ইহুদি শহীদত্বের জঘন্য বাণিজ্যিক ব্যবহারের চেয়ে?
লাইব্রেরি আর বইয়ের দোকানের তাক জুড়ে অগণিত বাজে মানের বই, যেগুলোতে আবেগ আর সত্যের চেয়ে বাজারের চাহিদা বেশি। আমার বাবার আজীবনের এক বন্ধু ছিলেন, যিনি আউশভিটজে তাঁর সহবন্দী ছিলেন- একজন আপোষহীন বামপন্থী আদর্শবাদী, যিনি নীতিগত কারণে যুদ্ধের পর জার্মান ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এই মানুষটি পরবর্তীতে ইসরায়েলের হলোকাস্ট জাদুঘর এর পরিচালক হন। অবশেষে, অনেক দুঃখ ও হতাশা নিয়ে, আমার বাবা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে এই মানুষটিও হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা কলুষিত হয়ে গেছেন, নিজের বিশ্বাসকে ক্ষমতা ও মুনাফার জন্য বিকিয়ে দিয়েছেন।
“হলোকাস্ট সারভাইভারদের গল্প”- সবাই যেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিল, সবাই যেন প্রতিরোধ যোদ্ধা- এগুলো লেখকের পরিবারের জন্য ছিল বিদ্রুপের উৎস। অনেক আগেই জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, যদি কোনো সত্যকে নিয়মিতভাবে প্রশ্ন না করা হয়, তাহলে সেটি শেষমেশ অতিরঞ্জনে মিথ্যায় পরিণত হয়।
লেখকের বাবা-মা প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশ করতেন, কেন তিনি নাৎসি গণহত্যার বিকৃতি আর শোষণ নিয়ে এত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট উত্তর হলো- এই ইতিহাসকে ব্যবহার করা হচ্ছে ইসরায়েলি রাষ্ট্রের অপরাধমূলক নীতিগুলোর পক্ষে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের যৌক্তিকতা হিসেবে। আজকের “হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রির” পক্ষ থেকে ইউরোপের কাছ থেকে “দরিদ্র হলোকাস্ট বেঁচে থাকা লোকদের” নামে টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা, সেই শহীদত্বের নৈতিক মহিমাকে নামিয়ে এনেছে মোন্তে কার্লোর এক ক্যাসিনোর স্তরে।
প্লেটো একবার মানবিকভাবে বলেছিলেন, “তুমি দুই বেদনাক্রান্ত মানুষকে তুলনা করে বলতে পারো না, কে বেশি সুখী।” আফ্রিকান-আমেরিকান, ভিয়েতনামি, আর ফিলিস্তিনিদের কষ্টের সামনে দাঁড়িয়ে, লেখকের মায়ের বিশ্বাস ছিল: “আমরা সবাই হলোকাস্টের শিকার।”
অলংকরণঃ তাইফ আদনান