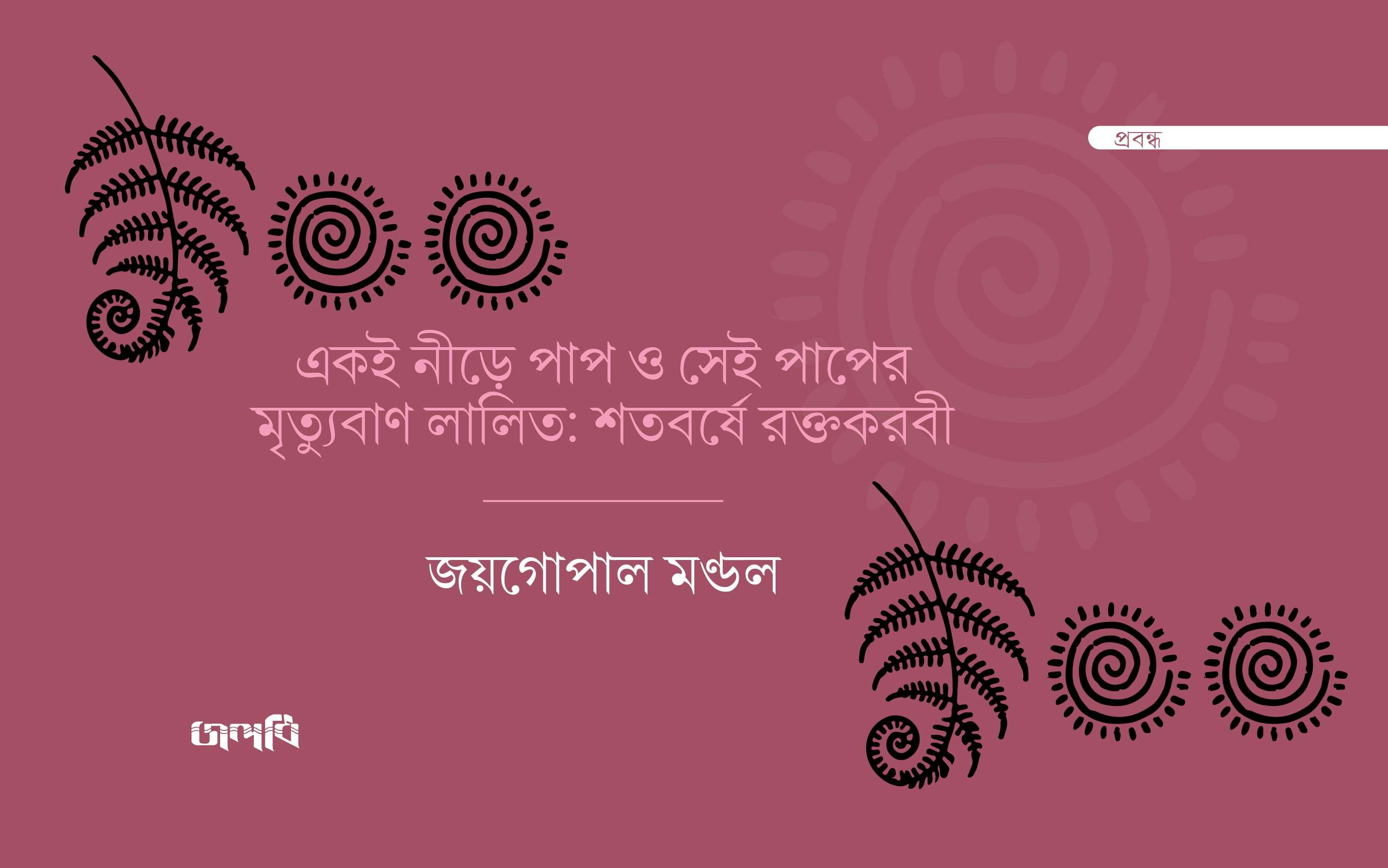
সবাই জানে ‘জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে’, তবুও নদীর বুক দখলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে লোলুপ রাজা। কবি জীবনানন্দ দাশের কথায় : “সাম্রাজ্য ভেঙে যায়, —/ হেমন্তের মেঘের মতো মিলিয়ে যায় সম্রাটের চিৎকার”। যুদ্ধের অবিস্মরণীয় পরিণাম জেনেও পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয়। কে জানত যে যাদের কোনো বোধ নেই তারাই রাজার সিংহাসনে বসবে। কবি জীবনানন্দ বুঝেছিলেন সত্য – ‘যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা’, ‘যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই – প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই / পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া’।
একবিংশ শতাব্দীর নির্বোধ প্রণয়নীদের মাঝে ভয়ংকর দুর্নীতিরাজ, দুষ্কৃতীরাজ— অমানবিক পাশবিক শাসন ব্যবস্থা। এই শতকে এক দুঃসময়ের মুখোমুখি সভ্যতা তথা বাঙালিও। শিক্ষকের মধ্যে যোগ্য ও অযোগ্যের দ্বন্দ্ব, শাসকের গদিতে অনিশ্চিত মানবতাহীন, প্রাণহীন, -পরাধীন জীবনের এক জটিল বৃত্ত --সাধারণ মানুষ নিজস্ব বৃত্তিতে, নিজস্ব মননে- চেতনায়, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকারহীন হতাশায় নিমজ্জিত, মানবতার বাণী, প্রাণের মূর্তি অবসিত জীবনের সমুদ্রের তরঙ্গে।
গণতন্ত্রের জয়োল্লাসে শিশুবলি প্রথার শুরু। এই বাংলায় এতদিন গণতন্ত্রের পূজার সময় নরবলি হত। এই যে শাসকের স্বৈরাচারী ছাপ-- ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষেও বাঙালি দেখেছে কিনা সন্দেহ। কবি জীবনানন্দের ভাষায়, "দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ।" এবং “এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়/ মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/ শুকুন ও শিয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"--এ কোন্ সকাল রাতের চেয়েও ঘন অন্ধকার; শিক্ষকেরা রাস্তায়; অর্থের বিনিময়ে অযোগ্যের হাতে শিক্ষালয়, এ নবীন শাসক হীরক রাজার দেশের মতো প্রকাশ্যে শিক্ষালয় বন্ধ করেনি ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। স্বাস্থ্যেও মহিলা-ছাত্রী তথা ডাক্তার কর্মস্থলে ধর্ষিতা হয়, খুন হয়। কিশোরীর বুক চিরে রক্ত খায় শাসকের চেলাচামুন্ডেরা, আর বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় রাজার মতো। এমন ভয়ংকর সংকটে যেমন মনে পড়ে সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র, তেমনি ফিরে দেখলে বোঝা যাবে শতবর্ষ পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্রোহের নাটক, প্রতিরোধের নাটক 'রক্তকরবী' আজও সমান প্রাসঙ্গিক, শাসকের বিরুদ্ধে গর্জমান রবীন্দ্রকণ্ঠ।
১৯২০-এর পর পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপ্রাণ লড়াই, অসহযোগ আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন —স্বরাজ দল গঠন(১৯২৩) এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ৭ম পাঠ চক্রের নোট, নভেম্বর ২০১৯-এ উল্লিখিত হয় — ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সক্রিয়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২১-২২ সাল থেকে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, কানপুর শহরকে কেন্দ্র করে পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন মুজাফফর আহমেদ, এস এ ডঙ্গে, শিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, গোলাম হোসেন প্রমুখ নেতারা। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে কানপুরে প্রথম পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – প্রভৃতির মাঝে শাসকের উগ্র হিংসাও সমানভাবে সক্রিয় ছিল--এরই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন 'রক্তকরবী' (আশ্বিন ১৩৩৩ /১৯২৬)। এই নাটক রচনার শতবর্ষ চলেছে - কী দুর্ভাগ্য, ব্রিটিশশাসন সমাপ্ত হলেও স্বাধীন ভারতবর্ষে এই নাটক বিস্ময়করভাবে যেন সমকালের প্রতিবিম্ব--নাটকের চরিত্রের কন্ঠে এমন সব সংলাপ ধ্বনিত হচ্ছে, সেই ঘটনাক্রমের মধ্যে উলঙ্গ রাজা-র স্বরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রদর্শিত হয়--- শাসকের তোষণ পদ্ধতি, শিল্পী সাহিত্যিককে সুকৌশলে শাসকের পদানত রাখার - নিয়োগের নেপথ্যে সম্পর্কের যোগসূত্র--- সবই সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত। সংলাপগুলো যেন এই সময়ের গর্ভ থেকে উত্থিত শব্দব্রহ্ম। কবি যেন সভ্যতার সংকটের কথা বলেন, তেমনি আবার উচ্চারিত হয় 'ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। নাটকের পরিসমাপ্তিও তাই, এক সময়ের রাবণ রাজার হৃদয়ে জেগে ওঠে মানবিক চেতনা।
‘রক্তকরবী’র রাজার মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ তাই রাবণ ও বিভীষণ দুই সত্তার সংযোজন করেছেন, রাজার মধ্যে যখন বিভীষণ সত্তা জেগে উঠেছে তখন আপনাকে আপনি পরাস্ত করেছেন--এটাই হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তব বড় নিষ্ঠুর--রাজার মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটে না, ঘটাতে হয়,--প্রয়োজন হয় রঞ্জনের-নন্দিনীর-বিশুপাগলের –জনতার--এদের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে রাজার বোধদয় ঘটে, পতন হয় রাজার। এই যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান ভারতের প্রক্রিয়া, কিন্তু এখনো যে রাজা সেই একই জালের আড়ালে তথা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ ঘরে থেকে জনগণের তাপ-উত্তাপ নেওয়ার চেষ্টা করে।
ব্রিটিশ শাসনে রাজা ছিলেন অদৃশ্য, আমজনতার থেকে বহুদূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। 'রক্তকরবী'র রাজা তাই ছিলেন অদৃশ্য, প্রকাশ্যে আসে না। এই বণিকী শাসক এসেছে এদেশের সম্পদ লুট করতে--- তার শাসনতন্ত্রে মানুষ মানুষ থাকেনি - মাটির তলা থেকে সোনার তাল তুলে আনার যন্ত্র। রাজা- নিজেই বলে, "নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছায়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না।"
-আসলে শাসক সবটা গ্রাস করতে চায়, বস্তু-অবস্তু সবই। কিন্তু অবস্তু তো প্রাণের আরাম, তা তো দেবতার দান, প্রকৃতিকে তো চাইলেই কারও অধীন করা না-সে হল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নন্দিনী, এক প্রতিবাদী মানবী মূর্তি। নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন,
"রক্তকরবী সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারি দিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।... মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়- মাটির উপরি তলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রাণের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সেই সহজ সৌন্দর্যের।"
—আর রাজা মাটির তলার ধন খুঁড়ে খুঁড়ে হয়ে উঠেছে রাবণ, সমগ্র পৃথিবীর যা কিছু গ্রাস করতে চায়। কবি রবীন্দ্রনাথ এই রাজার মধ্যে বিভীষণকেও আরোপিত করেছেন, তাই নন্দিনীর প্রাণের ছোঁয়ায় প্রাণের মাধুর্যও নিতে চায়। কারণ সেই যে সহজ সৌন্দর্য, আনন্দের দাম অনেক বেশি যক্ষের ধনের চেয়ে, গুপ্ত গৃহে প্রতাপ আছে প্রেমের পূণ্যতা নেই। 'রক্তকরবী' নাটকে তাই কবি প্রতাপের সঙ্গ প্রেমের দ্বন্দ্বে প্রেমকেই জয়ী করেছেন। একই রাজার আত্মায় বিবেকের জাগরণ ঘটিয়েছেন, ফলে ধ্বজাপূজার সময় রাজা নিজস্ব জাল ছিন্ন করে নেমেছেন প্রকাশ্য জনতার মাঝে। ফলে মুক্তি পেয়েছেন অধ্যাপক-সহ সকলে। এজন্য অবশ্য রঞ্জনের আত্মদানে রক্তকরবীর রাঙা পথ সূচিত হয়েছে। সমগ্র নাটকের সূচনা থেকেই দেখি নন্দিনী এসেছে প্রাণের বেগ নিয়ে, যন্ত্রকে আঘাত করতে —বার বার আঘাত করেছে, 'লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে' নারী শক্তির নিগূড় প্রচেষ্টায় রাজা রাবণ যেন বিভীষণ চেতনায় আপন সৃষ্ট কারাগারকে ভেঙে প্রাণের আবহকে বন্ধন মুক্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।
নাট্যকার তাই বলেছেন, "আদি কবির সাতকান্ডে স্থানভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরিতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একই দেহেই রাবণ ও বিভীষণ। সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে। "
এই রাজা বা রাবণের হাতেই আছে মায়ামৃগ বা সোনার হরিণ, যা প্রলুব্দধ করে আজও জনতাকে, শিল্পীকে, অধ্যাপককে, কবিকেও।
"অধ্যাপক। জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পন্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পন্ডিত।"
বর্তমানে বাংলার শিক্ষামন্ত্রীকে দেখলে একথা কি মনে হয় না? এই যে ভোগবাদী জীবনের লালসা— তাতেই বন্দি হয় বিবেকত্ব। যখন পাপের ভাঁড়ার পূর্ণ হয়, তখনই রাজা আপনাকে আপনি পরাস্ত করে।
কবি যখন এই নাটক লিখছেন তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হয়, এই ভারতবর্ষেও শুরু হয়েছে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই-এর তুফান হাওয়া, যা পৃথিবীর ইতিহাসের নব অভ্যুদয় রচনা করেছে--সেই আন্দোলনের প্রতীক রঞ্জন বা রক্তিম। হয়তো সেই প্রতিবাদের রং রক্তকরবীর রূপ ধরেছে।
নন্দিনী বলে, "জানি নে আমার কেমন মনে হয় আমার ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রং গলায় পরেছি, বুকে পরেছি হাতে পরেছি”
যক্ষপুরে রক্তকরবী যেখানে সেখানে মেলে না। কিশোর বলেছে, "রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।" -তথাকথিত শহরের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কারাগারে তথা যক্ষপুরীতে রক্তকরবী, প্রতিবাদের রাঙা প্রাণ সহজে মেলেনা, এ তো চিরন্তন। কারণ যক্ষপুরী কারা পরিচালনা করে? সর্দার দল : সর্দার মহারাজ, মেজ সর্দার, ছোট সর্দার, এদের সহযোগী ভন্ড গোঁসাই আর মোড়ল। বিশু পাগলের সাহসী কন্ঠে এদের অত্যাচারের স্বরূপ প্রকটিত হয় ঃ
“ঐ-যে ফাগু হতভাগা বারো ঘন্টার পরে আরও চার ঘন্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।"
"সর্দার কেবল যে ফেরার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা শুধু আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে"
কৃষির সভ্যতা কীভাবে যন্ত্রযুগের যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, বর্তমান প্রগতিশীল সভ্যতা যে তারই গণতান্ত্রিক রূপ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সোনার লোভে কবি-শিল্পী-শিক্ষক মেরুদন্ড বিকিয়ে শাসকের পদলেহনে মগ্ন, সে নারী শাসক হোক, কিংবা পুরুষ। আসলে শাসকের রূপ নারী হলেই কি পালটায়? না। বর্তমান বাংলা তথা সমগ্র পৃথিবীর বহু শাসকের একই নগ্ন-কদর্য রূপ প্রকাশিত, শুধুমাত্র বিবেকের চেতনাই তা ধরা পড়ে, কিন্তু সেই বিবেক, কিংবা নন্দিনির মতো প্রতিবাদী মানবী যদি অপহৃত হয়, বিলুপ্ত হয় সমাজ থেকে — কী হবে সেই সমাজের? ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শ্রমিক বিপ্লবের, শিক্ষক আন্দোলনের জন্য 'হীরক রাজার দেশে' উদয় পণ্ডিতরা বন্দি হয়নি। গোপনে গুহায় থেকে উত্তর প্রজন্মকে প্রতিবাদের মন্ত্র শিখিয়েছেন, রাজার যন্তর মন্তরে ঢোকালেও তাদের বিবেক জাগ্রত, তাই হীরক রাজার মধ্যে শুভোদয় ঘটে, নিজের মূর্তি নিজেই ভাঙে।
দেখা যাক যক্ষপুরীতে মানুষের অবস্থান কী ছিল---
বিশু বলেছে - "আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলাম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।"
ফাগুলাল বলে, "পিঠের কাপড়ে দাগা আছে আমি ৪৭ফ।"
আর সর্দারের বক্তব্যে এইসব অমানুষগুলোর জীবনযাত্রার হালহকিকত ফুটে ওঠে--- "যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা আছে।" "এদের ভালো কথা শোনাবার জন্য কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে।" — এই যে গোঁসাইজী, সে তো এই সময়ের তোলা আদায়ের যন্ত্র, আবার যন্ত্রমন্তরের বিজ্ঞানীও কি নয়? তাই গোঁসাই বাবা নামকীর্তনের ছলাকলায় ধমকিও দেন--- পড়ুন তো এই শব্দবন্ধগুলি কি একালের রাজার চেলাদের কণ্ঠস্বর নয়?
"বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া এখনো নড় নড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানিং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো কটা মাস পাড়ায় ফৌজি রাখা ভালো। কেননা ফৌজের কাজে অহংকারটা দমন হয়, তারপরে আমাদের পালা।" — এই যে ফৌজ, সে কি বর্তমান পুলিশ প্রশাসন নয়? যাদের প্রশাসনিক কাজে গণতান্ত্রিকতা তো দূরের কথা, এদের উর্দির সঙ্গে রাজনৈতিক রং মিলে যাচ্ছে: যখন যেই শাসক আসে তারই রঙে রাঙিয়ে নেয়। শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশশাসন ব্যবস্থায় যা যা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তা যেন আজও সতত প্রযোজ্য। স্বাধীন ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক পোশাকে রাবণ রাজা বিরাজমান, যাতে নন্দিনীর মতো মানবীর ছোঁয়ায় বিবেক জাগ্রত হবে তবেই গদি থেকে টানিয়ে নামাবে জনগণ।
এবার দেখি চাকরি দেবার রাজনীতি কেমন ছিল রাজতন্ত্রের যুগে ব্রিটিশ শাসনে? একটা নমুনা দেখা যাক,
"মোড়ল। প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়ই মনে দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্য আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচিকুমড়োর----
সর্দার। আচ্ছা, পরশু আসতে বলো, দেখা মিলবে।"
-এইরকম শাসনব্যবস্থার কারণে আজও তো হাজার হাজার চাকরীপ্রার্থী রাস্তায়, আবার হাজার হাজার চাকরিহারা অশ্রু নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের বুটের লাথি খাচ্ছে। এক অদ্ভুত চিত্র 'রক্তকরবী' নাটকের রন্ধে প্রতিধ্বনিত--- শাসকের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে শাসকপন্থীরা জানলেও যে প্রতিবাদের রং গায়ে মাখতে পারে না, তার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। নন্দিনী যখন তার ভালোবাসার রঙ খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে সময় দু'রকম ছবিতে রাজনীতির বর্তমান রূপ ধরা দেয়; আবার শাসকপন্থীদের যে চোখ আর কান বন্ধ করে কাজ করতে হয় তার পরিষ্কার বক্তব্য লক্ষ্য করা যায় :
"নন্দিনী। ওগো লালটুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছো?
প্রথম। সেদিন রাতে শম্ভুমোড়লের বাড়িতে দেখেছি।
নন্দিনী। এখন কোথায় আছে সে?
দ্বিতীয়। ঐ-যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছায় না।"
লক্ষণীয় 'লালটুপিরা' যারা সরকার বিরোধী (সেই সময়ের), হয়তো বা সদ্য সংগঠিত বামপন্থীরা, তাই সরকারের অন্দরের খবর জানে না। অথচ দায় এড়িয়ে বক্তব্য রাখে। এদের অন্তরে শাসকপক্ষের ছবি - সর্দারনীদের কথা, চিরকালীন চিত্র :
" নন্দিনী। ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জান।
প্রথম। চুপ চুপ।
নন্দিনী। তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বলতেই হবে।
দ্বিতীয়। আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিকে আছি।"
-এই যে নাট্যচিত্র একি অবাস্তব? নাকি নির্ভেজাল ও নির্মম বাস্তব? আজকের যুগেও রাজার অনুচরের কিংবা শাসকপন্থীর বিবেক জাগ্রত হয় তাহলেই তাকে খুন হতে হয়, তাই টিকে থাকতে হলে, সোনার তালসহ লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতে গেলে, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, পথশ্রী, যুবশ্রী পেতে গেলে চোখ বন্ধ রাখতে হয়, কানে তুলো গুঁজে আর মুখে কুলুপ এঁটে দিতে হবে। তাতে প্রাণের আরাম ও সৌন্দর্য না থাকলেও পশুত্বটুকু বাঁচিয়ে রেখে ভোগবাদী রসে হাবুডুবু থাকা যায়; বুদ্ধিজীবীরাও যেমন পুরস্কারের লোভে নিজেদের শাসকপন্থী করে তুলেছে; মান-হুঁশকে বিসর্জন দিয়ে।
শতবর্ষ পরেও 'রক্তকরবী'র প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এই নাটককে মঞ্চস্থ করলে নিশ্চিত যে শাসক তাদের প্রতি বিরাগভাজন হবেই। তবুও কি নন্দিনীরা চুপ থাকবে? তাই নিশিযাপনে রাত দখলের আন্দোলন সংঘটিত হয়, মানুষের মানববন্ধন হয়--- রাজা তুমি যতই উলঙ্গ হও তোমার লজ্জা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে এ বাংল, হে রাজা তোমার আসন একটা সময় ছিনিয়ে নেবে। হে হীরক রাজা অথবা রাণী সাবধান হও, শেষের সেদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ নন্দিনীরা আজও জাগ্রত, বুক ফুলিয়ে বলে, "আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।" ‘বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক নড়ব না।" এই যে ‘রক্তকরবী’র নন্দিনীর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সে তো মৃত্যুঞ্জয়ী।
বিরোধীদের জয়ডঙ্কা প্রতিটি যুগেই শাশ্বত, অপরাজেয়। তাই রাজা বলতে বাধ্য হয় - " আমি যৌবনকে মেরেছি--- এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।" - এই যে রাজার পরাজয়, এ-তো নিয়তি নয়, প্রাকৃতিক, মানবিক সত্য। অনুভূতির পবিত্রতায় সিদ্ধ করে, তখন শাসকের কঠিন হৃদয়ে জেগে ওঠে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার সাধ, চাই মুক্তি। কবি রবির চেতনায় রাজা তাই বলে- " আমার এই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক--- তাতেই আমার মুক্তি।" মানব সভ্যতার দুর্ভাগ্য এই-- যে রাজা হয় তার অন্তরাত্মায় রাবণ মুর্ত হয়ে ওঠে, আর যখন শাসনে শাসনে, অত্যাচারে পীড়নে সাধারণ নাগরিক গর্জে ওঠে নন্দিনীর প্রাণোন্মদায়, তখন রাজার মধ্যে হিল্লোল তোলে বিভীষণের বোধ, পতন হয় রাজার। ‘রক্তকরবী’ যে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, চেতনার জয়ধ্বজা উড্ডীন করার নাটক। শতবর্ষ পরেও শোনে আপামর জনগণ - "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে / আয় আয় আয়।"
কৃষি সভ্যতাকে উপড়ে ফেলে শিল্পের জোয়ার আসতে পারে না, কৃষিকে ভিত্তি করে চলুক সৃষ্টির প্লাবন এটাই হোক সমগ্র বিশ্বের প্রার্থনা। কবিগুরুর কথায় তাই চিরন্তন বাণীর সার্থক রূপ প্রকাশিত - "রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন, তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তার বীণা বাজল।"
রক্তকরবী রঞ্জনের প্রিয়, নন্দিনীর অলংকার, রঞ্জন-রঙে রাঙা প্রতিবাদ, তার মৃত্যুতেই সে মৃত্যুঞ্জয়ী, তাই রাজা নিজেকে নামিয়ে এনেছে প্রাণের আনন্দ নিতে, বাস্তববাদী জীবন থেকে, ধনতান্ত্রিক লোভ থেকে, বেরিয়ে জীবনের স্বাদ নিতে, মুক্তির উন্মুক্ত উল্লাস কী যে আনন্দ দেয় ---- জঞ্জালের মধ্যে ফুটে ওঠা রক্তকরবীর মধ্যেই আছে সে আনন্দ, শ্রমিকের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিবাদের রং রক্তকরবী, শ্বেতকরবী নয়। সে তো শান্তির দূত। জগদ্দল পাথরকে সরাতে ভেঙে ফেলতে চায় রক্তকরবী-নন্দিনী, রঞ্জনের উপস্থিতিতেই ঘটে, তাকে হত্যা করলেই শত শত রঞ্জন বেরিয়ে আসে নন্দিনীর উদ্বেল উত্তাল তরঙ্গে—
নন্দিনী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ঐ যে আলো মুক্তির, ফাটা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে, কঠিন পাথরকে ভেঙে আসে, প্রাণহীনের মধ্যে আসে প্রাণের স্পর্শ, মনুষ্যত্বের মুক্তি ঘটানোর জন্যই নন্দিনী বা নীরব নারী শক্তির লড়াই--- নামহীন মানুষগুলোর মধ্যে মনুষত্ব জাগরণের চেষ্টা করেছেন নন্দিনী, রাজাও ফিরে পেয়েছে মান- হুঁশ। যুগে যুগে এভাবে আত্মজাগরণের গীত ধ্বনিত হলেও রাজার চরিত্র বদলায় না। এটাও কি গণতন্ত্রের পরম্পরা? গণতান্ত্রিকতা কি কেবলই অলংকার? যা নিয়ে জনগণ অহংকার করে। কবির বাণীতেই প্রত্যাশার কথা বলি,
“তুমি আলো
যেইখানে সাগর নীলিমা আজ মানুষের সন্দেহে কালো
ভাইরা ব্যথিত হ’লে ভাইদের ভালো ,
মানুষের মরুভূমি একখানা নীল মেঘ চায়।" ( জীবনানন্দ দাশ /তুমি আলো)
হে রাজা বা রাণী শোনো মানুষের কান্না, হাহাকার, যে সততার প্রতীক নিয়ে এসেছিলে সেই মরমী রূপে ফিরে এসো মাটিতে, সেখানে মানুষ বড়ো কাঁদছে--- ‘একখানা নীল মেঘ’ দাও ‘মানুষের মরুভূমি’তে।
মনে রেখো বিশ্বকবির বাণী :
“ এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল;
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।”
হে রাজা তোমারও ইতিহাস লেখা হয়ে আছে সৃষ্টি ও সমাজের বিকেলের সূর্যাস্তের গভীর অন্ধকারে। “অনেক রাজার শাসন ভেঙে গেছে /অনেক নদীর বদলে গেছে গতি”, তুমি এইবেলা খুঁজে নাও অনন্ত সকাল। সবারই জীবনে আলোর প্রয়োজন, যে আলো ছড়িয়ে আছে ‘রক্তকরবী’ নাটকের শুরু থেকে শেষ। মহৎ দার্শনিকের এই যে চিন্তার সঞ্চারণ তা জীবনের মহৎ পথ। মাঝে মধ্যে মনে হয় যেভাবে দুধসাগরে হাবুডুবু খায় তথাকথিত চিন্তার তরঙ্গ, কী লাভ নক্ষত্রের আসা যাওয়া! সত্যি সবটাই কি মিথ্যে হয়ে যাবে? না হতেই পারে না, মানুষ এখনও কাহিনি রচনা করে। এই প্রত্যয় মর্মরিত করে তোলে বিস্রস্ত অগ্নির লেলিহান শিখা। বাঁচবে পৃথিবীর মানুষ —এটাই চিরন্তন, কালজয়ী, অন্তত ইতিহাস তাই শেখায়। শতবর্ষে ‘রক্তকরবী’ পাঠ সেই আত্মজাগরণের পথ সৃষ্টি করে।
অলংকরণঃ তাইফ আদনান

