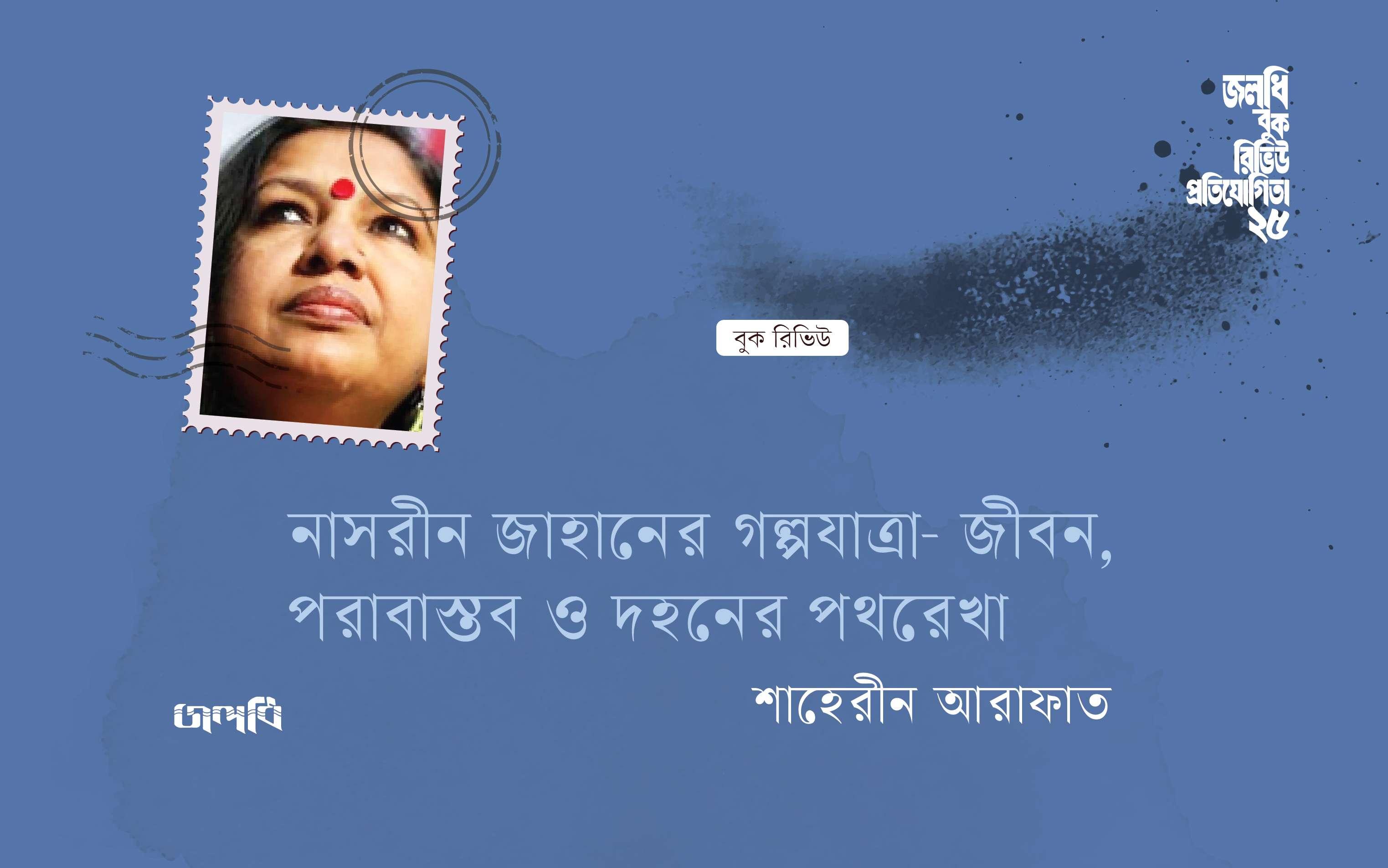
জীবন এক অদ্ভুত যাত্রা, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত নতুন ঘটনা, নতুন চিন্তা, নতুন সান্নিধ্যের আহ্বান। কখনো হাসি, কখনো কষ্ট; কখনোবা বিমূর্ত তার মায়া। এই উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়ার খেলায় জীবনের গুঢ় রহস্য উন্মোচিত। আমাদের সামনেই তার হাতছানি; তবু অধরাতেই যেন এক বীভৎস সৌন্দর্য। জীবনের এই অব্যক্ত, সাধারণ অথবা অতিন্দ্রীয় কোনো কালপর্ব ধরা পড়ে সাহিত্যিকের চোখে, যা তিনি শিল্পের মাধুর্যে, শব্দের বুননে তুলে ধরেন পাঠকের সামনে- মনের অন্তঃস্থলে জাগায় সে অনন্য মায়া, নিউরনের ছোটাছুটি। ছোটগল্পের পরিধি খুব বিস্তৃত হয় না। কার্যত সাহিত্য যখন পাঠকের মধ্যে চিন্তার খোরাক জোগায়, তখনই তা পূর্ণতা পায়।
ছোটগল্প হলো জীবনের একটি খণ্ডাংশের বর্ণনা, যেখানে উপন্যাসের মতো সামগ্রিক জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয় না। এটি বাহুল্যবর্জিত, রসঘন, নিবিড় এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সাহিত্যরূপ। এতে সীমিত সংখ্যক চরিত্র, নাটকীয় আরম্ভ ও প্রাক্কাল এবং একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা পরিস্থিতির ওপর জোর দেওয়া হয়।
ছোটগল্প প্রসঙ্গে ১৮৯৪ সালের ২৭ জুন শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আজকাল মনে হচ্ছে যদি আমি আর কিছু না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে।’ অর্থাৎ, ছোটগল্পে গল্পকার একইসঙ্গে যে অনুভূতি আস্বাদন করেন, তা পাঠকের মাঝেও বিলিয়ে দেন। আর সেই আবেগ-অনুভূতি সংরক্ষিত রাখেন মনের কুঠরিতে, যা সূক্ষ্মভাবে কোনো বিশেষ মুহূর্ত বা কালপর্ব নিয়ে ভাবতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
দুই.
নাসরীন জাহান আমাদের সাহিত্য জগতে নব্বই দশক ও পরবর্তী কালপর্বের উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী। এখনো নিরলস সাহিত্যচর্চায় রত আছেন। তিনি গল্পের মানুষ, উপন্যাসের মানুষ, এমনকি নাটক আর লিটলম্যাগেরও মানুষ। ১৯৯৪ সালে ‘উড়ুক্কু’ উপন্যাসের জন্য তিনি অর্জন করেন ‘ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার’। পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য নাসরীন জাহান লাভ করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার। তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশের পরিসর ছাড়িয়ে বিশ্বপরিমন্ডলে প্রসারিত হয়েছে। পেঙ্গুইন থেকে বেরিয়েছে তাঁর উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ। অন্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে তাঁর লেখা।
সাহিত্যিক জীবন, কাল ও পারিপার্শ্বিকতা দেখেন মনের চোখ দিয়ে। অনুভবের চাদরে তিনি সমস্তকে জড়িয়ে এক নতুন বাস্তবতার জন্ম দেন। এতে তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে জুড়ে থাকে নিজস্ব লেখনী। একেকজন লেখকের প্রবণতা একেকরকম। নাসরীন জাহানেরও নিজস্ব শৈলী, নিজস্ব রসবোধ রয়েছে। আবার গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি- এই তিন সত্তার ভেতর নাসরীন জাহান নিজেকে একাকার করেছেন। তাঁর মতে, শিল্প-সাহিত্যের রূপগুলো একে-অপরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন জড়িয়ে থাকে। এক লেখায় (‘সাহিত্য নিয়ে এক স্লিপ’, কথাসাহিত্যিকের ফেসবুক থেকে) নাসরীন জাহান বলেন, ‘শিল্পের একটি শাখার সাথে আরেকটর সূত্র স্বর্ণলতার মতো জড়িয়ে থাকে। শিল্পের সব মাধ্যমের জন্য আমার দৃষ্টিতে তিনটা বিষয় খুব জরুরি। এক. পঠন। দুই. মানুষ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। তিন. দলীয় পক্ষপাতিত্ব থেকে অন্তত প্রকাশ্যে মুক্ত থাকা।’
তবে আমার ব্যক্তিগত পছন্দ তাঁর ছোটগল্প। এসব গল্প একেকটা উপন্যাসেরই প্রাককথন যেন! তবে ছোটগল্পের সব রূপ, রস, মাধুর্য্য এতে নিহিত। ২০০২ সালে অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত ‘নির্বাচিত গল্প’ গ্রন্থের ভূমিকায় নাসরীন জাহান লিখেছেন, ‘...এক সময় আমি উপন্যাসের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বিচরণ করতে করতে অনুভব করি, সবচাইতে কঠিন গল্প লেখা। একটি গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হাঁটা যায় না। একটি বিস্তৃত বিষয়কেও কমপেক্ট করে সেখানে একটি পরিধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। সেই কঠিন পথে হাঁটা আমি ছাড়িনি। ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করেছি গল্প নিয়ে বহুমাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার, যে নিরীক্ষার ফাঁকে আটকে থাকে যে-কোনো শিল্পের চিরায়িত সত্য-প্রাণ, সেটা যেন না হারায়।’
একজন কথাশিল্পী তখনই সজীব, প্রাণময় থাকেন; যখন তিনি নতুন চিন্তা, নিরীক্ষার মধ্যে থাকেন। আর এ কারণে নাসরীন জাহানের সাহিত্য আজও মূর্ত বাস্তব- তারুণ্যের বাহক। প্রেমের গল্প হোক বা পরাবাস্তব- তাঁর সাহিত্যকর্মে নিরীক্ষাপ্রিয়তার ছাপ স্পষ্ট। আমাদের চারপাশের ঘটনা আর চরিত্রকে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে এনেছেন। এ কারণেই তাঁর গল্পে খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন সমাজের বহুমাত্রিক সম্পর্কের কথা। এই সম্পর্কগুলো তাঁর সৃষ্টি নয়; বরং তিনি তা শিল্পকর্মে তুলে এনে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন; ভাবতে বাধ্য করেছেন- সেই চরিত্রগুলো আমাদেরই অংশ।
তিনি ঘটনার বর্ণনা করেন কাব্যিকতা প্রয়োগে, ভাষার প্রাঞ্জল শৈলীতে। চরিত্রগুলো জীবন্ত, তাদের চালনা করছেন না; যেন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যই তাদের একে-অপরের সঙ্গে সম্পর্কের সেতু রচনা করছে। আর সাহিত্য ও সাহিত্যিক সেখানে চরিত্রগুলোর মধ্যকার সেই সেতু। পাঠক সেই বাস্তব বা পরাবাস্তব নিজের মাঝে অনুভব করেন চিন্তার আতিশয্যে। মানুষের জীবন, জীবিকা, প্রেম, যৌনতার স্বাভাবিকতা নাসরীন জাহানের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
তাঁর সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কও এক জটিল সমীকরণে বাঁধা। পাঠক সৃষ্টির কোনো কৌশলে তিনি যাননি। আবার পাঠকের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাও নেই তাঁর। পুরস্কার, সম্মাননার মায়ায় তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। তাই বাজারের কাটতি তাঁকে ছুঁতে পারেনি। সৃষ্টিশীলতার মাঝেই তিনি সাহিত্য নির্মাণ করেছেন ও করছেন।
২০২২ সালে জলধি থেকে প্রকাশিত হয়েছে নাসরীন জাহানের ‘গল্পসমগ্র-১’। এখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য পাঁচটি গল্পগ্রন্থ যুক্ত রয়েছে- ‘স্থবির যৌবন’, ‘বিচূর্ণ ছায়া’, ‘সূর্য তামসি’, ‘পথ হে পথ’ ও ‘সারারাত বিড়ালের শব্দ’। মোট গল্পের সংখ্যা ৩৪। ২০২৪ সালে একই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় ‘গল্পসমগ্র-২’। এখানে তাঁর তিনটি গল্পগ্রন্থ যুক্ত রয়েছে- ‘আশ্চর্য দেবশিশু’, ‘পুরুষ রাজকুমারী’ ও ‘সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে’। মোট গল্পের সংখ্যা ৩২। এই পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধে মূলত এই গল্পগুলোতে কথাসাহিত্যিক নাসরীন জাহানের প্রবণতা ও শিল্পগঠন নিয়ে সংক্ষিপ্ত পাঠ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলো।
তিন.
নাসরীন জাহানের গল্পগুলো পাঠ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর বয়ান ও গঠনশৈলীর ভিন্নতা। তিনি প্রচলিত ধারার মতো সাজানো-গোছানো কাহিনি নির্মাণে আগ্রহী নন। কারণ তাঁর গল্প যে জীবন ও সমাজকে বহন করে, তা নিজেই বিশৃঙ্খল, ভাঙাচোরা ও অনিয়মে ভরা। ফলে গল্পেও সেই বিশৃঙ্খলা ও অগোছালো স্রোতকে অবধারিতভাবে জায়গা করে দিতে হয়। বাস্তব জীবনের টানাপড়েন, মানুষের দেহ-মন, কামনা-বাসনা, সমাজের শেকল- সবকিছুই মিলেমিশে তাঁর গল্পে রূপ নেয়। এ কারণেই নাসরীন জাহানের গল্প একদিকে সামাজিক বাস্তবতার নির্মম প্রতিবিম্ব; অন্যদিকে মানবচেতনার গভীরতম অন্ধকার কোণের অনুসন্ধান।
নাসরীন জাহান ‘দাহ’ [গল্পগ্রন্থ ‘স্থবির যৌবন’] যখন লিখেন, তখন তিনি কলেজের শিক্ষার্থী। অথচ কী সুতীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি ও চিন্তা সেখানে ফুটে উঠেছে! গল্পটি আমাদের নিয়ে যায় দগ্ধ শরীরের যন্ত্রণা ও সামাজিক নির্দয়তার ভেতর। যুবক হাফিজের পোড়া শরীর শুধু একজন ব্যক্তির কষ্ট নয়; বরং তা হয়ে ওঠে ক্ষমতাধরদের অবহেলা, গরিব মানুষের অস্বীকৃত অস্তিত্ব এবং মৃত্যুপূর্ব বিভীষিকার প্রতীক।
সেবার ধানকাটা শেষে প্রভাবশালী তালুকদারের ধান পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল হাফিজের ওপর। একরাতে কাটাধানে আগুন লাগে, ঘুমন্ত হাফিজ ভীষণভাবে দগ্ধ হয়। তালুকদার তাকে চিকিৎসা না করিয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে জোরাজুরি করতে থাকে। পোড়া শরীরের হাফিজ গ্রামে যেন এক দর্শনীয় প্রাণীতে পরিণত হয়।
গল্প থেকে- ‘হাফিজ চোখ বুজতে গিয়ে থমকে যায়, যে মহিলাটি এতক্ষণ কলকল করছিল, সে হাফিজের দিকে একগাঁদা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে প্রায়। অন্য মহিলাগুলোও ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরা তো রোজই হাফিজকে দেখে। আজ এমন চমকে ওঠার কারণ খুঁজতে গিয়ে হাফিজ নিজের ফেঁপে ওঠা শরীরটা দেখে। মহিলাগুলো নাকে আঁচল চেপে দ্রুত সরে যেতে থাকে। হাফিজের বুকটা একটা জ্বালাময়ী অস্বস্তিতে ছেয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে, এক রাতের মধ্যেই তার এমন পরিবর্তন এসেছে, যা তাকে হুঁকো, জলচৌকির মতো স্বাভাবিক আর জড় করে রাখছে না। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে।’ [পৃষ্ঠা ১৫-১৬, গল্পসমগ্র-১]
মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হাফিজের স্বপ্ন-বাস্তব বিভাজন ঘুলিয়ে যায়, আর তার শরীর এক অচেনা অবসাদে বিলীন হয়। গল্প থেকে- ‘শরীরের ক্ষতস্থানগুলো এমনভাবে জ্বলতে থাকে, মনে হয়- ওর শরীরটা কেউ ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে কুচিকুচি করে ফেলছে। আকাশের দিকে মুখ করে দম নেওয়ার চেষ্টা করে সে। এরপর শুরু হয় দেহের মর্মান্তিক কম্পন। সে যন্ত্রণায় ইটের গুঁড়ো চেপে বিড়বিড় করে- আল্লাহ মরণ দাও। আল্লা গো...। শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা যেন ওর কলজের ভেতর এসে জমা হয়।’ [পৃষ্ঠা ১৯-২০, গল্পসমগ্র-১] এ গল্প কেবল একজন কৃষিশ্রমিকের মৃত্যুর আখ্যান নয়; বরং সমাজের অবিচার ও মানুষের যন্ত্রণার প্রতি আমাদের নির্মম উদাসীনতার এক নগ্ন চিত্র।
ধর্ষণজনিত গর্ভপাত আর নারী-অস্তিত্ব সংকটের প্রতিফলনেই ‘কাঁটাতার’ [গল্পগ্রন্থ ‘সূর্য তামসি’] গল্পের পটভূমি নির্মিত। এই আখ্যান প্রথম দৃষ্টিতে এলোমেলো বলে মনে হলেও গভীরে গেলে দেখা যায়- যেখানে জীবন ও মন, সংসার ও সমাজ নিজেরাই অনিশ্চয়তায় ভরা, সেখানে লেখকের কাছে গল্পকে কড়াকড়ি শৃঙ্খলায় বাঁধা সম্ভব নয়। চরিত্র ও তার চারপাশের অনিবার্য বাস্তবতা ধরতে গিয়ে নাসরীনের ভিন্ন কোনো উপায়ও ছিল না। ধর্ষিতা নারীর দেহবোধ, যৌন তৃষ্ণা বা মাতৃত্বের শূন্যতা- এসবের মধ্য দিয়েই তিনি তুলে ধরেছেন সমাজ-অস্বীকৃত অথচ গভীর সত্য কিছু বিষয়।
কুন্তলার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে বলা যায়- যে নারী দাম্পত্যে যৌন তৃপ্তি পাননি, যার অস্থির দেহ সবসময় তৃষ্ণার্ত থেকেছে, তার এমন অনুভূতিকে কি অপরাধ বলা যায়? সমাজ হয়তো অপরাধ বলবেই। কিন্তু মানুষকে তার কামনা-বাসনা, অধিকার ও মর্যাদা থেকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজ কাঠামো কতটা টেকে? মানবাধিকারের দায় কি আংশিক হলেও সমাজের ঘাড়ে বর্তায় না? অথচ বাস্তবে দেখা যায়, সমাজ মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাকে বঞ্চিত করে কুন্তলার শাশুড়ির মতো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লেখক এমন সমাজকে এক বৃদ্ধ, ক্লান্ত, কিন্তু প্রভাবশালী বিধান হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। এ কারণেই সম্ভবত নাসরীন জাহান চোখের সামনে বেড়ে ওঠা গ্রাম্যকন্যা কুন্তলার জীবনে আসা অন্ধকার অধ্যায়কে কেন্দ্র করে মাতৃত্বের স্বপ্নময় আলোকময়তার আভাস সৃষ্টি করেছেন।
‘পুরুষ’ [গল্পগ্রন্থ ‘বিচূর্ণ ছায়া’] গল্পে আমরা দেখি প্রতিবন্ধী বুলুর ভেতরের অস্থিরতা। সে জন্মগতভাবে ল্যাংড়া। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও সামাজিক অবহেলা তাকে দমিয়ে রাখলেও ভেতরে সে তরুণ পুরুষ, কামনা-বাসনা ও মর্যাদার দাবিতে পরিপূর্ণ। চারপাশের অবজ্ঞা, পরিবারের বৈমাত্রেয় বোনের উসকানিমূলক আচরণ তাকে ক্রমে ক্ষুব্ধ ও সহিংস করে তোলে। শেষপর্যন্ত মৃত্যুকামনায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে সে। এখানে নাসরীন জাহান দেখিয়েছেন- কীভাবে এক তরুণ জীবনের অবদমিত যৌবন ও অসম্মানের ক্ষত ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। গল্পটি কেবল এক প্রতিবন্ধী ছেলের বেদনা নয়; এটি পুরুষত্ববোধ, স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা ও আত্মঘাতী প্রতিক্রিয়ার জটিল মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান।
চার.
নাসরীন জাহানের গল্পভুবনকে বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই স্পষ্ট হয়, তাঁর সৃষ্টির অন্যতম কেন্দ্রীয় অনুষঙ্গ হলো মৃত্যুচেতনা। তবে এই মৃত্যু কেবল জৈবিক সমাপ্তি নয়; বরং মানুষের অন্তর্লীন যন্ত্রণার, অপরাধবোধের, আত্মদহন ও সামাজিক অবহেলার বহুমাত্রিক রূপক। তাঁর গল্পে মৃত্যু উপস্থিত হয় কখনো বিমূর্ত দার্শনিক প্রশ্ন হয়ে, কখনো ভৌতিক বা জাদুবাস্তব চিত্র হয়ে, আবার কখনো সমাজ-ধর্মের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে চরিত্রের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে। তাঁর গল্পে সুবিমল মিশ্র ও এডগার অ্যালান পো’র ছায়া পাওয়া যায়। তবে তিনি এই নিরীক্ষামূলক ধারাকে আত্মস্থ করে নিজের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছেন মৃত্যুর এক ভিন্নতর ভাষ্য।
‘বিবসনা’ [গল্পগ্রন্থ ‘বিচূর্ণ ছায়া’] গল্পে লেখক মৃত্যুকে সরাসরি মূল বিষয় করেননি, তবে সমাপ্তি এসেছে মৃত্যু ভারাক্রান্ত এক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। কেন্দ্রীয় চরিত্র যুবক হোসেন আলী, পিতা ও হুজুরের শাসনে সে ধার্মিক হিসেবে বেড়ে ওঠেছে। তবে হোসেন আলীর কাছে এই জীবন ছিল এক ধরনের বন্দিশালা। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা নয়; বরং মৃত্যুভয় ও শাস্তির আতঙ্ক তাকে বেঁধে রেখেছিল। যৌবনে এসে নারীপ্রেমের আকর্ষণ সেই শেকল ভাঙতে চাইলেও তার মুক্তি শেষমেষ মেলে যৌনকর্মীর কাছে আত্মসমর্পণে।
গল্প থেকে- ‘হোসেন আলী ছুটতে ছুটতে কোনোকিছু চিন্তা না করেই একটা বেড়ার ছোট খুপড়িতে উপস্থিত হয়। তারপর সেই ছায়া অন্ধকার দরজায় শরীরের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আঘাত করে। দরজা খুলে দিয়ে তৃষ্ণার চোখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আসে। ক্লান্ত শরীর টেনে হোসেন আলী সেই ঘরে প্রবেশ করে। বিস্ময় কেটে যাওয়ার পর সহজ রমণীটি হোসেন আলীর চোখ থেকে পাঠশোলার বেড়াটি সরিয়ে নেয়। সরিয়ে নেয় ত্যানার মতো ল্যাপটে থাকা পাতলা আবরণটিও। বেড়াটি, আবরণটি অন্তর্হিত হওয়ার পর পরই হোসেন আলী আশ্চর্যজনকভাবে উপলব্ধি করে- তার এতদিনকার দ্বন্দ্ব, কৌতূহল, মানসিক যন্ত্রণা কপূরের মতো হাওয়ায় উবে যাচ্ছে।’ [পৃষ্ঠা ১১৯-২০, গল্পসমগ্র-১]
তবে প্রশ্ন থেকেই যায়- এ মুক্তি কি সত্যিই মুক্তি, নাকি এক সম্ভাবনাময় সত্তার অপমৃত্যু? গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে এরকম একটি বাক্য দিয়ে- ‘মৃত্যুর মতো চেপে বসা দেহের এক অলৌকিক ভার এক গভীর গহ্বরে ঢেলে অন্য এক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে হোসেন আলী নিঃসাড় হয়ে ওঠে।’ [পৃষ্ঠা ১২০, গল্পসমগ্র-১] নাসরীন জাহান এই গল্পে ধর্মীয় ভীতির বিপরীতে মানবিক কামনা ও শরীরী তৃষ্ণার সংঘাতকে স্পষ্ট করেছেন।
‘রজ্জু’ [গল্পগ্রন্থ ‘বিচূর্ণ ছায়া’] গল্পের কেন্দ্রবিন্দু চাঁদউদ্দিনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট। এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পর তার ভেতরে জমে ওঠা অবদমন, যৌনচাহিদা, অপরাধবোধ ও স্মৃতির ঘন জটিলতা ভেসে ওঠে। বাবার মৃত্যুর কল্পিত চিত্র থেকে শুরু করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ হারানো পর্যন্ত, সব মিলিয়ে চাঁদউদ্দিন পরিণত হয় বিভ্রমগ্রস্ত এক চরিত্রে। স্বাধীনতা লুপ্ত হবে বলে চাঁদ সংসারের পাঁকে জড়ায়নি। কিন্তু সাতচল্লিশ বছর বয়সে এসে এজন্য তার ভেতরে ভেতরে খানিকটা অনুশোচনাও হয়। চাঁদউদ্দিনের বন্ধু সতীনাথ ঘরে এক যৌনকর্মীকে নিয়ে আসে ভোগের জন্য। মেয়েটিকে দেখে পছন্দ না হলেও খানিক সময় পর তাঁর সান্নিধ্যে যায় চাঁদউদ্দিন।
গল্পের শেষ দুটি লাইন- ‘তার শরীর ঠান্ডা হয়ে জমে আসছে। তার আয়ত্তের মধ্যে থলথলে মোটা রমণীর বুক থেকে যেন ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠছে। এবং তার কতক্ষণ পরই আশ্চর্যজনকভাবে মেয়েটি রাজপথে পড়ে থাকা দোমড়ানো থেঁতলে যাওয়া নারীতে রূপান্তরিত হয়।’ [পৃষ্ঠা ১৩২, গল্পসমগ্র-১]
গল্পের অস্পষ্ট সমাপ্তি- সে কি সত্যিই খুন করল, নাকি কেবল বিভ্রমে ডুবে গেল- এই প্রশ্নই নাসরীন জাহান পাঠকের মনে জাগিয়ে দেন। ফলে মৃত্যু, কামনা, বিভ্রম ও অপরাধবোধ একাকার হয়ে যায় এই আখ্যানের বুননে।
পাঁচ.
নাসরীন জাহান মূলত মানবজীবনের ‘অন্তর্বাস্তবতা’র শিল্পী- যে ভেতরের ভূগোলটি ভয়, লজ্জা, আকাঙ্ক্ষা, অপরাধবোধ, মৃত্যুচেতনা আর নিষিদ্ধ তাড়নায় ভরা। তাঁর গল্পে অস্তিত্ববাদী অনিশ্চয়তা, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একইসঙ্গে কাজ করে: চরিত্ররা বহির্জগতে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল- সেখানে দমবন্ধ দ্বন্দ্ব, পুনরাবৃত্তিময় স্মৃতি, ক্লেদ ও ক্ষয়ের দীর্ঘ ছায়া মিলে মিশে থাকে। এই অন্তর্মুখী অভিযানই শেষ পর্যন্ত মানবতাবাদী জীবনজিজ্ঞাসায় গিয়ে মিশে, কারণ মুক্তির যে আর্তি তিনি শুনতে পান- তা আসলে মানুষের মর্যাদারই আরেক নাম।
আশির দশকের সংকলনগুলো- ‘বিচূর্ণ ছায়া’ (১৯৮৮), ‘পথ, হে পথ’ (১৯৮৯), ‘সূর্য তামসী’ (১৯৮৯)- এ লেখক একদিকে প্রথাগত বর্ণনাশৈলী রপ্ত করেছেন, অন্যদিকে মনোবিকলনঘন বিশ্লেষণাত্মক কৌশলও তীক্ষ্ণ করেছেন। ‘অভ্যাস’, ‘দাহ’, ‘পাখিওয়ালা’, ‘পথ, হে পথ’, ‘বিলীয়মান হলুদ নীল স্বপ্নগুলো’, ‘কাঁটাতার’, ‘প্রেতাত্মা’, ‘খোলস’, ‘নিশাচর’-এসব গল্পে গ্রামীণ ও নাগরিক অভিজ্ঞতার উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ, ছিমছাম বাক্যগতি ও সরল সময়রেখার ভেতর মনস্তাত্ত্বিক স্পর্শ জুড়ে দেন; ফলে কাহিনি এগোয়, কিন্তু প্রতিটি ঘটনায় চরিত্রের ভিতরের ঢেউ আলাদা করে শোনা যায়। নব্বইয়ের দশকে ‘সারারাত বিড়ালের শব্দ’ ১৯৯১, ‘পুরুষ রাজকুমারী’ ১৯৯৬, ‘সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে’ ১৯৯৭ সেই প্রবণতা আরও নিরীক্ষামুখী হয়েছে- কোথাও প্লট ভেঙে কোলাজ, কোথাও দীর্ঘ দৃশ্যপটের উপর জোর, কোথাও আবার ভৌতিক-জাদুবাস্তব মিশে এক ধরনের অদ্ভূত আবছায়া। এই ধারাটি সবচেয়ে স্পষ্ট ‘সুন্দর লাশ’, ‘কুকুর’, ‘বিকার’, ‘ল্যাম্পপোস্টের নিচে’, ‘সারারাত বিড়ালের শব্দ’, ‘অস্পষ্ট আলোর ছবি’ প্রভৃতি গল্পে।
‘সুন্দর লাশ’ [গল্পগ্রন্থ ‘বিচূর্ণ ছায়া’] গল্পে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বজ্ঞ বয়ানের সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী। গল্পের মূল চরিত্র সুশান্ত ও জিনাত। সংকটের কেন্দ্রে আছে আকর্ষণ ও অনাসক্তির অস্বাভাবিক গতিবিদ্যা। জিনাতের ‘পুরুষালী বলিষ্ঠতা আছে’ বলেই সুশান্ত তাকে বিয়ে করে; কিন্তু ক্রমেই অনাসক্তি কাজ করতে থাকে। জিনাত অনুভব করে নারীর চেয়ে সুন্দর পুরুষের প্রতি সুশান্ত বেশি আকর্ষণ বোধ করে।
এক মৃত যুবককে কেন্দ্র করেই সুশান্তর যৌন মনস্তত্ত্বের সক্রিয় প্রকাশ ঘটে। শহরের বাইরে জ্যোৎস্নারাতে ওই যুবকের মরদেহ ছেড়ে আসতে রাজি হয় না সুশান্ত। ক্ষুব্ধ জিনাত গাড়িতে উঠে ফিরে আসার মুহূর্তে-
‘জিনাত দেখে সুশান্তর মুখটা হুবহু সেই মৃত যুবকের মুখ হয়ে গেছে, দু’চোখে আগুন জ্বলছে। দু’লাফে জিনাত জিপের মধ্যে এসে বসে। তারপর দ্রুত হাতে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে ঘোর-লাগা চোখে দেখে জ্যোৎস্না রাতের উজ্জ্বল আলোয় মৃত যুবকটি উঠে দাঁড়িয়েছে। আর সুশান্ত তাকে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মতো আদর করছে।’ [পৃষ্ঠা ১০১, গল্পসমগ্র-১]
‘কুকুর’ [গল্পগ্রন্থ ‘বিচূর্ণ ছায়া’] গল্পে শৈশবের আতঙ্ক, ল্যাম্পপোস্টের আলো-ছায়া, নীরব রাত- সব মিলিয়ে এক পরাবাস্তব ন্যারেটিভ গড়ে ওঠে। শৈশবের কুকুরভীতি ছিল যে মেয়েটির সে নির্জন রাস্তায় প্রত্যক্ষ করে ভীতিকর ছায়া, ল্যাম্পপোস্টের আলোয় প্রত্যক্ষ করে বিচিত্র দৃশ্য।
‘মেয়েটি ধূসর চোখে দেখে- সুন্দর ফুলগুলো, এতক্ষণ যারা নৃত্য করছিল, তারা বিস্ময়ে চেয়ে আছে। এবং তার স্বপ্নের পায়রা-বাড়ীটি শুভ্র ডানা মেলে শূন্যের উপর উঠে পড়েছে। মেয়েটি ধূসর চোখে দেখে- অসংখ্য কুকুরের ঘেউ ঘেউ, অসংখ্য রাত্রির অন্ধকার আক্রমণ এবং অসংখ্য মশার গুনগুনের মধ্য দিয়ে তার কোঁকড়ানো চুল ও ক্ষতের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মেয়েটির শেষ চুল বিন্দু একসময় নগরের সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির মধ্যে ডুবে যায়।’ [পৃষ্ঠা ১৪৪, গল্পসমগ্র-১]
এই রূপকচিত্রে মেয়েটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নিষ্পাপ, স্বপ্নবাহী সত্তার; যে কিনা শহুরে সহিংসতা, নির্যাতন, অন্ধকার ও যন্ত্রণার জালে আটকা পড়ে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফুল, পায়রা-বাড়ি, কোঁকড়ানো চুল তার স্বপ্নময় অস্তিত্বকে বোঝাচ্ছে; আর কুকুর, অন্ধকার, মশা ও চোরাবালি বোঝাচ্ছে দমনমূলক বাস্তবতাকে। ফলে এই চিত্রটি আসলে স্বপ্নের মৃত্যু ও মানবিক সত্তার অবলুপ্তির এক গভীর রূপক।
‘ল্যাম্পপোস্টের নিচে’ [গল্পগ্রন্থ ‘সূর্য তামসি’] গল্পে রয়েছে খণ্ড খণ্ড চিত্রের কোলাজ; যেখানে জীবনের দ্বন্দ্ব আর মৃত্যুবোধ এক সুতোয় গাঁথা। জন্ডিসে মৃত একটি দেহ ডাস্টবিনে পড়ে আছে, যা ধীরে ধীরে রূপ নেয় অদ্ভুত প্রাণীতে। এই প্রাণী মানুষ ও পশুর মিলিত রূপ- যেমন মানুষ ও পশু উভয়ই বর্জ্যভুক। লেখক নিজেই বলেছেন, এটি জাদুবাস্তবের চরিত্র, যা নগরের অবহেলিত মানুষের প্রতীক। এখানে মৃত্যু শেষ কথা নয়; বরং অবহেলিত জীবনের এক বিকৃত পুনর্জন্ম। মুশতাক আহমেদের ছেলে পাপ্পু জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। এজন্য সে নিজের পাপকে দায়ী করে। গল্পগ্রন্থ থেকে- ‘স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে হতাশ গলায় মুশতাক আহমেদ বলে, জরিনা আমি কিছুতে আর শান্তি পাই না। জীবনে পাপ একটু বেশিই করা হয়ে গেছে। ছেলেটা মরে এটাই প্রমাণ করে দিয়ে গেল।’ [পৃষ্ঠা ১৫০, গল্পসমগ্র-১] নিজের ছেলেকে হারানোর অপরাধবোধে পীড়িত হয় মুশতাক এবং সেই অদ্ভুত প্রাণীর মধ্যে মৃত সন্তানকে চিনতে চায়। তাকে ঘরে নিয়ে যায়; কিন্তু প্রাণীটি গৃহজীবন প্রত্যাখ্যান করে আবার ডাস্টবিনেই ফিরে যায় প্রাণীটি। গল্পে মৃত্যু, পাপবোধ ও জীবনের অবমাননা একাকার হয়ে নগর-বাস্তবতার এক মর্মস্পর্শী কোলাজ সৃষ্টি করেছে।
‘বিলীয়মান হলুদ নীল স্বপ্নগুলো’ [গল্পগ্রন্থ ‘সূর্য তামসি’] গল্পে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবক আত্মনিপীড়নের পথে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। তার ভেতরে জন্ম নেয় মৃত্যুকামনা, যা তাকে আত্মহানির দিকে ঠেলে দেয়। জটিল মানসিক সংকট, প্রেমের ব্যর্থতা ও পারিবারিক দমনচর্চা তাকে আত্মঘাতী করে তোলে। গল্পে মৃত্যুর উপস্থিতি প্রথমে বিভ্রম ও আতঙ্ক হিসেবে ধরা দেয়- যেন পরলোকের জিজ্ঞাসা- কিন্তু শেষাবধি মৃত্যু হয়ে ওঠে এক শান্তির আকাঙ্ক্ষা। নাসরীন জাহান এখানে দেখিয়েছেন, জীবনের যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু অনেক সময় বেশি সহনীয় ও সুন্দর বলে মনে হতে পারে।
‘একটি দীর্ঘশ্বাসের ডালপালা’ [গল্পগ্রন্থ ‘সারারাত বিড়ালের শব্দ’] হলো জাদুবাস্তব ঘরানার এক অনন্য গল্প, যেখানে মৃত্যুচিন্তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে দার্শনিক স্তরে উন্মোচিত হয়। ওমর নামে এক যুবক দুই বন্ধু কায়সার ও টুলুর সঙ্গে রাতে গরুর গাড়িতে গ্রামের পথ ধরে যাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে এক জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে। সেখানে ওমরের সঙ্গে দেখা হয় এক বৃদ্ধের। বৃদ্ধ চরিত্রটি তার জীবনের নৃশংস কাহিনি অকপটে বলে যায়- যেখানে বিকলাঙ্গতা, সামাজিক অবহেলা, বিবাহের অপমান এবং শেষপর্যন্ত নিজ সন্তানকে হত্যা পর্যন্ত আছে।
বৃদ্ধ কদাকার চেহারা, বিকৃত হাত-পা নিয়ে জন্মেছিল। তাকে সবাই ভয় পেত, করুণা করত। তার ছেলেও একইরকম বিকৃতি নিয়ে জন্মেছিল। যে শিশুকে বৃদ্ধ নিজ হাতেই হত্যা করেছিল। এখানে মৃত্যু কেবল একটি জীবনের সমাপ্তি নয়; বরং বংশপরম্পরায় বিকৃতির উত্তরাধিকার বন্ধ করার এক নৃশংস প্রচেষ্টা। গল্পটি দেখায়, মৃত্যু কখনো কখনো মুক্তি বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিকৃত যুক্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর সেই কৃতকর্মের অনুশোচনা আত্মহননের পথে ধাবিত করতে পারে।
গল্প থেকে- ‘ওরা যখন সন্তানের হত্যার জন্য ক্রমাগত নির্যাতন চালাচ্ছে, তখন একরাতে আমি আবার নতুন বোধ দ্বারা আক্রান্ত হই। মনে হয়, আমার সন্তানের পা দু’টো বিকলাঙ্গ হলেও দুটি সুন্দর হাত ছিল তার। ফলে সে যে শুধুই অন্যের গলগ্রহে পরিণত হতো সেটা হয়তো ঠিক নয়। আমি একটি সুন্দর অট্টালিকার কথা স্মরণ করি, যার ভাঁজে ভাঁজে আছে বালু। খাঁজ মিশ্রিত অনন্ত বালুর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি। সব এলোমেলো হয়ে যায়। পাগলের মতো হয়ে যাই আমি। নিজেকে রূঢ় হিংসুটে হত্যাকারী মনে হয়। মনে হয় আমি আমার ব্যর্থতার ভার আরেকটি প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। অথচ আকৃতির অভিন্নতা সত্ত্বেও তার মাথা কিংবা হাত দুটি থেকে নতুন কিছুর জন্ম হতে পারত। অতদূর হয়তো দৃষ্টি প্রসারিত করার নিজেই ছিঁড়তে থাকি... আমি বুঝতে পারি, তাকে বাঁচিয়ে রাখলে কুণ্ঠিত হয়ে বেঁচে থাকার শান্তি সে একা পেত না। তার দিকে যাদের চোখ পড়ত, ঘৃণায় যারা সরিয়ে নিত চোখ, শান্তি তাদেরও কিছু কম হতো না। একটি বিকৃত কিছু চোখের সামনে দুলছে... বোঝো কেমন শাস্তি! যা হোক জেল স্থানান্তরের সময় আচমকা গাড়ি থেকে আমি নিচ দিকে লাফিয়ে পড়ি... পাক খেতে খেতে আমার দেহটা গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। আমি আত্মহত্যা করি... বলতে বলতে বৃদ্ধ দাঁড়ায়... এবং উচ্চারণ করে... কী হবে এই গল্প শুনে? একসময় জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতের পথ ধরে সে হাঁটতে থাকে। একটা তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে যায় ওমর। তার যেন স্পষ্ট মনে হয়... হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো, আত্মহত্যাই তো করেছিল... ওমর কাঁপতে থাকে। বৃদ্ধ পেছন দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো উচ্চারণ করে... বিশ্বাস করো না, এর কিছুই বিশ্বাস করো না...। তারপর তার দেহটা বিশাল প্রান্তরের সবুজের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। ওমর দেখে একটি ভঙ্গুর মানুষ ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নার গহ্বরের মধ্যে মিলে যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে না তাকে।’ [পৃষ্ঠা ২৯৫-৯৬, গল্পসমগ্র-১]
যে কোনো খ্যাতিমান লেখকের সাহিত্যেই কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুচিন্তার বিশেষ প্রভাব থাকে। নাসরীন জাহানের গল্পগুলো একসঙ্গে পড়লে বোঝা যায়, মৃত্যুচিন্তাকে তিনি নানা মাত্রায় অনুসন্ধান করেছেন। কোথাও মৃত্যু আসে নগরের প্রান্তিক জীবনের অবমাননা হিসেবে, কোথাও আসে আত্মদহন ও আত্মগ্লানির মধ্য দিয়ে, কোথাও তা নৃশংস দার্শনিক সিদ্ধান্তে, আবার কোথাও প্রতীকমূলক চিত্রকল্পে কিংবা সরাসরি অস্তিত্ব সংকটে। এই বহুমাত্রিক মৃত্যু-বর্ণনা প্রমাণ করে, নাসরীন জাহান একদিকে আধুনিক শহর ও সমাজের ভেতরে মৃত্যুর অমানবিক বাস্তবতাকে ধরেছেন, অন্যদিকে মানবমনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে মৃত্যুচেতনাকে এক বিমূর্ত ও দার্শনিক উচ্চতায় তুলে এনেছেন। তাঁর ভাষা, কল্পনা ও জাদুবাস্তবের ব্যবহার মৃত্যু-ভাবনাকে দিয়েছে তীব্র আবেগ ও শিল্পিত উজ্জ্বলতা। ফলে তাঁর গল্পে মৃত্যু সমাপ্তি নয়; বরং জীবনের অর্থ ও অসারতা অন্বেষণের একটি দার্শনিক দরজা।
ছয়.
নব্বইয়ের দশকে ‘সারারাত বিড়ালের শব্দ’ গল্পগ্রন্থে নাসরীন জাহান পরীক্ষার মাত্রা আরও তীব্র করেছেন। ‘অস্পষ্ট আলোর ছবি’ গল্পে চিত্রশিল্পী নীলিমার মানসিক বিপর্যয় কাহিনির মূল অবলম্বন। সে প্রেতাত্মাকে আহ্বান করে, অস্বাভাবিক সব স্বপ্ন দেখে, এবং সেই বিভ্রম, আতঙ্ক, বিকার তার আঁকায় রঙ ও রেখার আকারে রূপ পায়। ফলে নীলিমার ক্যানভাস আর কোনো নিরপেক্ষ শিল্পের প্রতীক থাকে না; বরং তা তার অসুস্থ মনস্তত্ত্বের প্রতিরূপক হয়ে ওঠে।
এখানে নাসরীন জাহান মূলত মানুষের অবচেতন স্তরের বিশ্লেষণ করেছেন। নীলিমার ভেতর জমে থাকা ভয়, দুঃস্বপ্ন এবং অস্বাভাবিক চিন্তার প্রবাহ শিল্পে রূপ নেয়। এর ফলে গল্পে এক পরাবাস্তব পরিবেশ গড়ে ওঠে; যা ভৌতিক, রহস্যময় এবং অচেনা। নীলিমা আসলে আধুনিক নগরজীবনের এক মানসিক রোগী; তার ক্যানভাস যেন অবচেতনের আয়না, যেখানে অস্বাভাবিকতা শিল্পরূপ পেয়েছে।
‘একগুচ্ছ অন্ধকার’ গল্পে আর কোনো প্রচলিত কাহিনী নেই; বরং পরিবেশ ও মানসিক বাস্তবতা গল্পটিকে চালিত করে। দুই বছর পরে ঘরে ফেরা একজন মানুষের চোখ দিয়ে আমরা দেখি অদ্ভুত এক পরিবেশ, যা ধীরে ধীরে আতঙ্ক, বিকার ও অস্তিত্ববিনাশী অনুভূতিতে ভরে ওঠে। সাতটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এ গল্পে কোনো প্রথাগত কাহিনী নেই। আছে অন্ধকার, ভয়ভীতি, আতঙ্ক, রক্তপাতের বিচিত্র অনুষঙ্গ তৈরি করা এক অচেনা দুর্জ্ঞেয় বাস্তবতা। আর এর কেন্দ্রে আছে ছায়ার প্রকাশ। এই ছায়া আসলে আত্মপরিচয়ের বিভ্রান্তি, নিজের ভেতরের ভয় ও অন্ধকারের বহিরাবয়ব। গল্পকার এখানে এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পরীতি ব্যবহার করেছেন, যেখানে চরিত্রের ভেতরের মানসিক টানাপড়েন বহির্জগতে বিকৃত রূপে প্রতিফলিত হয়। আমরা দেখতে পাই, নাসরীন জাহানের আধুনিক শিল্পনিরীক্ষা শুধু কাহিনির ভেতরে নয়; বরং মানুষের ভেতরের অদৃশ্য মানসিক অস্থিরতাকে প্রকাশ করার এক বিশেষ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তিনি গল্পে মানুষের অবচেতন ও অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। ‘অস্পষ্ট আলোর ছবি’-তে তা এসেছে চিত্রশিল্পীর ক্যানভাসে, আর ‘একগুচ্ছ অন্ধকার’-এ তা এসেছে ছায়ার ভীতিকর রূপকল্পে। দু’ক্ষেত্রেই তিনি প্রচলিত গল্প বলার ধারা ভেঙে মনস্তত্ত্ব, বিকার ও পরাবাস্তবতাকে কাহিনির চালিকা শক্তি বানিয়েছেন।
‘শাদা ভাস্কর্য’, ‘টবের অশ্বত্থ’, ‘আলো পাথরের টান’- এ সব গল্পেও কাহিনির কেন্দ্র সরে গিয়ে স্থান নেয় মানস-ভূদৃশ্য; ঘটনা নয়, প্রতিক্রিয়াই মুখ্য। গল্পগুলোতে নাসরীন জাহানের শিল্পরীতির ভিন্ন অথচ পরস্পর সম্পর্কিত দিককে উদঘাটন করে। এসব গল্পেই বাস্তবতার বাইরের স্তর- অবচেতন, মানসিক বিকার, আতঙ্ক ও পরাবাস্তবতা- গল্পের বুননে প্রবল হয়ে ওঠে।
‘খোঁড়া দৌড়বিদ’ [গল্পগ্রন্থ ‘পুরুষ রাজকুমারী’] তেজী, প্রতিভাবান অথচ অহংকারী এক মানুষের পতনের গল্প। গল্পকার স্পষ্ট করে তুলেছেন তার ভেতরের উন্মত্ত আত্মবিশ্বাস এবং অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য- ‘অত কীসের ফষ্টিনষ্টি গপ্পো পাশের বাড়ির বৌ-ঝিগোর লগে? দূরত্ব রাখবি, ওরা তোর সমান?... বেবাকের লগে গা মিশায়া চললে ওরা আমারে সাদারণ মনে করব।’ [পৃষ্ঠা ১৫৪-৫৫, গল্পসমগ্র-২] এই দৃষ্টান্তে ফুটে ওঠে প্রতিভাবান মানুষদের এক পরিচিত দুর্বলতা- নিজেকে আলাদা করে রাখার মানসিকতা। কিন্তু নাসরীন জাহান এখানে কেবল অহংকারের পতন ঘটাননি, তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার ভূমিকা থেকেও চরিত্রটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। বিকলাঙ্গ হয়ে হাসপাতালে যাওয়া- সবই চরিত্রটির অহংকার ভাঙার কাহিনি। অথচ লেখক শেষ অব্দি তার অনুকম্পা বাঁচিয়ে রাখেন- ‘সে তারপরও হাঁটত, সবার মশকরার মুখেও তার উদ্ধত মাথা নিচের দিকে নামত না। মানুষের মন্তব্য সম্পর্কে তার অভিমত ছিল, মানুষ বড় বিচিত্র।’ [পৃষ্ঠা ১৫৬, গল্পসমগ্র-২] এখানে পতনের মাঝেও মানুষের আত্মসম্মান ও বাঁচার আকাঙ্ক্ষার একটি মানবিক ব্যাখ্যা মেলে।
‘এক রাতে, রেস্তোরাঁয়’ [গল্পগ্রন্থ ‘আশ্চর্য দেবশিশু’] গল্পে লেখক নগরজীবনের আনন্দ-উৎসবের ভেতর লুকিয়ে থাকা এক ধরনের শূন্যতা ও বিপন্নতা তুলে ধরেন। ইংরেজি নববর্ষে নাগরিকদের উল্লাস, রিকশাওয়ালাদের আনন্দ, কিশোরদের উচ্ছ্বাস দেখে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভাবে- ‘প্রতিদিনের শহর যদি এমন হতো?’ [পৃষ্ঠা ৭৫, গল্পসমগ্র-২] কিন্তু বাস্তবে সে দেখতে পায়, পুরনো বছরের বোঝা, নতুন বছরের হিসাব-নিকাশ, এবং মানুষের কৃত্রিম উল্লাসের ভেতর ফাঁকফোকর রয়ে গেছে। নাগরিক আনন্দ-আয়োজনে ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা ও অনাগ্রহও যেন প্রতিফলিত হয় এই কথায়- ‘যেকোনো ভাবে হোক বাঙালি ফুর্তি করছে, সে নিজেও করতে পারলে নিজেকে তার ভাগ্যবান মনে হতো।’ [পৃষ্ঠা ৭৬, গল্পসমগ্র-২] এখানে নাসরীন জাহান সাধারণ মানুষের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন।
‘জীবন্মৃত’ [গল্পগ্রন্থ ‘সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে’] গল্পে নাসরীন জাহান মানবজীবনের চরম সীমান্ত- জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বকে এক অনন্য শৈলীতে রূপ দিয়েছেন। আবুল হক, যিনি মৃত্যুশয্যায় ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় পড়ে আছেন, তার স্ত্রী আয়েশা বিশ্বাস করে দরবেশ চাচার ফুঁ বা খতমে ইউনুসের প্রার্থনায় স্বামী সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন; কিন্তু নাটকীয় মোড়ে আয়েশা নিজেই মৃত্যুবরণ করে। আর আবুল হক অনুভব করেন নিজের ভেতরে অদ্ভুত এক সঞ্চারণ। গল্পকার গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে- ‘পরদিন ভোরে আয়েশা মারা যায়। ডিমের খোসার মতো ঝকঝকে সকাল। মৃতপ্রায় আবুল হক হঠাৎ অনুভব করেন, তাঁর হাতপা শরীরের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অজস্র কম্পনের মধ্যে হাসনাহেনার গন্ধ আজ যেন আতর। লাশটির দিকে কঠিন চোখে তাকান তিনি... রাতে এটা কি স্বপ্নের কথা বললো আয়েশা? তারপর তার এই আচমকা মৃত্যু? সব কি সেই দরবেশ চাচার কাজ? তবে কি এটাই সত্য, একটি মৃত্যুর বদলে তিনি বেঁচে উঠবেন? ভয়ে সম্ভাবনায় আবুল হকের হৃৎপিণ্ড তেল নিঃশেষিত কুপির মতো দপ্দপ্ জ্বলতে থাকে।’ [পৃষ্ঠা ২৭৮, গল্পসমগ্র-২] মৃত্যু ও জীবনের এই অদলবদল যেন মানুষের অনিশ্চয়তার চিরন্তন প্রতীক হয়ে ওঠে।
সাত.
নাসরীন জাহানের গল্পে মানবজীবনের বহুমাত্রিক অন্তর-বাস্তবতা, ব্যক্তির অহংকার ও ভাঙন, সমাজের তাগিদ ও অনুকম্পা যেমন প্রকাশ পায়; তেমনি আবার কখনো মনস্তত্ত্বের অন্ধকার ও পরাবাস্তবতার গূঢ় প্রবাহ লক্ষ্যণীয়। তিনি কখনো বিশ্লেষণাত্মক নিরীক্ষা, কখনো এক্সপ্রেশনিস্ট বহির্বাস্তবের প্রয়োগ, আবার কখনো সমাজমনস্তত্ত্বের মানবিক আর্তি ও অনুরণন দিয়ে গল্পকে নির্মাণ করেছেন। ফলে তাঁর গল্পগুলো কেবল কাহিনি নয়; বরং মানুষ ও সমাজের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক রূপকল্প হয়ে ওঠে।
ভাষার দিক থেকে নাসরীন জাহানের শৈলী বহুমুখী; আবার সংযত- ছোট বাক্যে ছেদহীন গতি যেমন আছে, তেমনি আছে কৌতুকহীন নির্মমতার সামনে হঠাৎ কাব্যিক চমক। অলংকারের ব্যবহার কম’ কিন্তু ইমেজারি প্রখর- চোখ, রক্ত, হলুদ, সবুজ, ল্যাম্পপোস্টের আলো, মাছির গুঞ্জন, বিড়ালের শব্দ- এগুলো বারবার ফিরে এসে এক ধরনের ‘ইনার অ্যাকুস্টিকস’ বা মানুষের অন্তর্জগতের শব্দ-প্রকৃতি- যেমন অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্মৃতি, ভয় বা স্বপ্নের ধ্বনি তৈরি করে; পাঠক সেই শব্দ-দৃশ্যের ভেতর দিয়ে চরিত্রের অবচেতন শুনে ফেলেন। বয়ানের কণ্ঠও স্থির নয়- সর্বজ্ঞ বর্ণনা থেকে সীমিত সর্বজ্ঞতা, চরিত্র-মনোলগ থেকে মুক্ত পরোক্ষ বচন- সবই কাজে লাগে অন্তর্জগতের বাস্তবতা দৃশ্যমান করতে।
জীবন ও ইতিহাস হলো দ্বন্দ্বের অবিরাম গতি। প্রতিটি অবস্থার ভেতরেই থাকে তার বিরোধ, আর সেই বিরোধের সংঘাত থেকেই জন্ম নেয় নতুন রূপ। যেমন ব্যক্তি চায় স্বাধীনতা, আবার সমাজ চায় শৃঙ্খলা। ব্যক্তি চায় ভালোবাসা ও আত্মপ্রকাশ, কিন্তু রাষ্ট্র চায় কর্তব্য ও আনুগত্য। নাসরীন জাহান তাঁর ছোটগল্পের ভূখণ্ডে সেই দ্বান্দ্বিকতার টুকরোগুলো এক স্বতন্ত্র ভৌগোলিকতায় উপস্থাপন করেন- যেখানে কাহিনির বাইরে আরেকটি কাহিনি চলে- স্বপ্ন, স্মৃতি, বিভ্রম, কামনা, ট্রমা আর মৃত্যুভাবনার। নারীবাদ বা জীবন-সংগ্রাম এখানে শুধু প্রতিরোধের অভিধান নয়; বরং মানবতাবাদেরই গভীর সংস্করণ। জাদুবাস্তবতা তাঁর কাছে পালানোর জানালা নয়; বরং বাস্তবের অস্বস্তিকর সত্যকে তীব্র আলোয় টেনে আনার উপায়। এজন্যই নাসরীন জাহানের গল্পে মৃত্যু শেষ কথা নয়- বরং সেই দরজা, যেখান দিয়ে আমরা মানুষের অন্তরখানা দেখতে পাই। হারানোর মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি জীবনের সীমা। সীমাকে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই আমরা খুঁজে পাই অসীমের আভাস। এটাই জীবনের প্রকৃত দ্বন্দ্ব- সীমা ও অসীমের মিলনে মানুষ নিজের স্বাধীনতা ও সত্তা নির্মাণ করে।
অলংকরণঃ তাইফ আদনান

